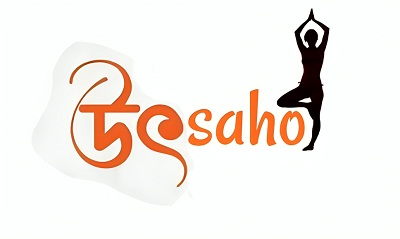ভারতবর্ষ, Chapter- 15, Class-9, SEBA
‘ভারতবর্ষ, Chapter- 15, Class-9, SEBA
৩. ক্রিয়া কলাপ
(ক) শুদ্ধ উত্তরটি বেছে নাও:
(১) লেখক কত বছর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন?
Ans. (২) দশ-এগারো
(২) বৃদ্ধ সাপ খেলানো সুরে কী পড়ছিলেন?
Ans. (৪) রামায়ণ
(৩) বৃদ্ধের ঠাকুরদা কোথায় ‘রামায়ণ’ গ্রন্থটি কিনেছিলেন?
Ans. (২) বটতলায়
(৪) কত বছর পূর্বে লেখক কলকাতায় এসেছিলেন বলে জানিয়েছেন?
Ans. (৩) পঁচিশ বছর
(খ) শূন্যস্থান পূর্ণ করো:
১। আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে।
২। বৃদ্ধ গদিতে বসে বিপুলকায় একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কি পড়তো।
৩। নাকের উপর মস্ত এক চাঁদির চশমা।
৪। আমার ঠাকুরদাদা বটতলায় এটি কিনেছিলেন।
৫। ধীর গম্ভীর দৃষ্টিতে আমায় আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিল।
(গ) শুদ্ধ-অশুদ্ধ বেছে বের করো:
১। এই সেদিন দৈবক্রমে ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম।
Ans. অশুদ্ধ (শুদ্ধ: এই সেদিন দৈবক্রমে বেড়াতে বেড়াতে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম।)
২। সেতু বাঁধা হচ্ছিল তাই আমি শুনেছিলুম।
Ans. অশুদ্ধ (শুদ্ধ: সেতু বাঁধা হচ্ছিল তাই আমি জেনেছিলুম।)
৩। বুড়ো কী পড়ছে জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হল।
Ans. শুদ্ধ
৪। বৃদ্ধকে অভিবাদন করে দোকান ত্যাগ করলাম।
Ans. শুদ্ধ
৫। ঠিক পঁচিশ বছর পূর্বে আমি এই ছেলেদের সামনে আপনাকে এই বই পড়তে দেখেছি।
Ans. শুদ্ধ
(ঘ) বাক্য রচনা করো:
* শুনতে শুনতে: বৃদ্ধের রামায়ণ পাঠ শুনতে শুনতে লেখক তন্ময় হয়ে যেতেন।
* বেড়াতে বেড়াতে: পঁচিশ বছর পর লেখক বেড়াতে বেড়াতে সেই পুরানো মুদিখানাটির সামনে এসে উপস্থিত হলেন।
* মিটমিট: আগেকার কলকাতায় রাস্তার ধারে মিটমিট করে গ্যাসের বাতি জ্বলত।
* আপাদমস্তক: বৃদ্ধ লেখককে আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিলেন।
* স্মিতহাস্যে: বৃদ্ধ স্মিতহাস্যে জানালেন যে বইটি তাঁর ঠাকুরদাদার কেনা।
* দিব্যচক্ষু: মুদিখানার অপরিবর্তিত দৃশ্য দেখে লেখকের মনে হল তিনি দিব্যচক্ষু পেয়েছেন।
* অভিবাদন: লেখক বৃদ্ধকে অভিবাদন করে দোকান ত্যাগ করলেন।
* Tradition (ঐতিহ্য): লেখক উপলব্ধি করলেন যে ভারতবর্ষের প্রকৃত ঐতিহ্য বা ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।
* অবশ্যম্ভাবী: লেখক কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছিলেন।
* বিপুলকায়: বৃদ্ধ গদিতে বসে একটি বিপুলকায় বই পড়ছিলেন।
* ক্রিয়াকাণ্ড: রামচন্দ্রের অপূর্ব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনে ছেলেরা আনন্দিত হত।
* ঘরকন্না: বৃদ্ধের মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে এবং তারা স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘরকন্না করছে।
* দৈবক্রমে: পঁচিশ বছর পর লেখক দৈবক্রমে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।
(ঙ) বাক্য সংকোচন করো:
* বৃহৎ আকারের- বিপুলকায়
* যাহা অবশ্যই ঘটিবে- অবশ্যম্ভাবী
* পা হইতে মাথা পর্যন্ত- আপাদমস্তক
* ছেলের বা মেয়ের মেয়ে সন্তান- নাতনি
* জানার জন্য বিশেষ আগ্রহ- কৌতূহল
৪. প্রশ্নাবলি (ভাববিষয়ক)
(অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন)
ক) ভারতবর্ষ পাঠটির লেখক কে?
উত্তর: ভারতবর্ষ পাঠটির লেখক এস. ওয়াজেদ আলী।
খ) লেখক কত বছর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন?
উত্তর: লেখক দশ-এগারো বৎসর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন।
গ) লেখকের বাসার নিকট কী ছিল?
উত্তর: লেখকের বাসার নিকটে একটি মুদিখানা ছিল।
ঘ) ‘Tradition’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘Tradition’ (ট্র্যাডিশন) শব্দের বাংলা রূপ হল ঐতিহ্য, অর্থাৎ পরম্পরাগত সংস্কার বা ভাবধারা।
ঙ) মুদিখানায় বসে বৃদ্ধটি কী পড়ছিলেন?
উত্তর: মুদিখানায় বসে বৃদ্ধটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়ছিলেন।
চ) লেখকের সামনে কীসের ছবি ফুটে উঠেছিল?
উত্তর: লেখকের চোখের সামনে প্রকৃত ভারতবর্ষের এক নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছিল।
ছ) বিপুলকায় বইটি কে, কোথা থেকে ক্রয় করেছিলেন?
উত্তর: বিপুলকায় বইটি (কৃত্তিবাসের রামায়ণ) বর্তমান বৃদ্ধের ঠাকুরদাদা বটতলা থেকে ক্রয় করেছিলেন।
জ) বৃদ্ধের পাঠের বিষয় কী ছিল?
উত্তর: বৃদ্ধের পাঠের বিষয় ছিল রামচন্দ্র কীভাবে কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছেছিলেন।
ঝ) বৃদ্ধটি কার লেখা কী বই পড়তেন?
উত্তর: বৃদ্ধটি কৃত্তিবাস ওঝার লেখা রামায়ণ বই পড়তেন।
৫. সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন
(ক) বৃদ্ধ রামায়ণের কোন অংশ পাঠ করতেন? ছেলে মেয়েদের মনে তার কী প্রতিক্রিয়া ঘটত?
উত্তর: বৃদ্ধ রামায়ণের সেই অংশটি পাঠ করতেন যেখানে রামচন্দ্র কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছেছিলেন। সেই অপূর্ব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনে ছেলেমেয়েদের মুখ আনন্দ, আগ্রহ আর উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠত।
(খ) লেখকের মতে পঁচিশ বছর পর কলকাতায় কী পরিবর্তন হয়েছিল?
উত্তর: লেখকের মতে পঁচিশ বছর পর কলকাতার নাগরিক জীবনের বহিরঙ্গে প্রভূত উন্নতি ও পরিবর্তন হয়েছিল। আগে যেখানে সাধারণ ঘর ছিল, সেখানে বড় বড় ম্যানশন (mansion) মাথা তুলেছে। আগেকার রিকশা ও ঘোড়ার গাড়ির বদলে রাস্তায় বড় বড় মোটর অনবরত যাওয়া-আসা করছে। এবং রাস্তার মিটমিট করে জ্বলা গ্যাসের বাতির জায়গায় এখন ইলেকট্রিক আলো স্থানটিকে দিনের মতো উজ্জ্বল করে রাখে।
(গ) ভারতবর্ষের নিখুঁত ছবি বলতে লেখক পাঠটিতে কী বুঝিয়েছেন?
উত্তর: ‘ভারতবর্ষের নিখুঁত ছবি’ বলতে লেখক ভারতবর্ষের সভ্যতার সেই আপন বৈশিষ্ট্যকে বুঝিয়েছেন, যা হল সাধারণ মানুষের সহজ-সরল ধর্মপ্রাণতা এবং অধ্যাত্মিকতা। তিনি বুঝিয়েছেন যে, বাইরের নাগরিক জীবনে যতই পরিবর্তন আসুক না কেন, ভারতবর্ষের মানুষের মনে বংশপরম্পরায় চলে আসা প্রাচীন সংস্কৃতির চিরন্তন ধারা বা ঐতিহ্য (Tradition) অপরিবর্তিত রয়েছে।
(ঘ) লেখক কী দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন?
উত্তর: পঁচিশ বছর পর সেই পুরানো মুদিখানাটির ভিতরকার দৃশ্য দেখে লেখক স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে, পঁচিশ বছর আগে যেমনটি দেখেছিলেন, ঠিক তেমনই একজন বৃদ্ধ গদিতে বসে রামায়ণ পড়ছেন, একজন মধ্যবয়স্ক লোক খদ্দের সামলাচ্ছে আর পাঠ শুনছে, এবং ঠিক আগের মতোই একটি খালি গায়ের ছেলে ও দুটি মেয়ে আগ্রহের সাথে সেই পাঠ শুনছে। এই অপরিবর্তিত দৃশ্য দেখেই তিনি স্তম্ভিত হয়েছিলেন।
(ঙ) ‘ভারতবর্ষ’ রচনাটির মূলভাব কী? মুদিখানা কীসের প্রতীক?
উত্তর: ‘ভারতবর্ষ’ রচনাটির মূলভাব হল, আধুনিকতা বা কালের পরিবর্তনে ভারতবর্ষের বাইরের রূপ বা নাগরিক জীবনের প্রভূত উন্নতি ঘটলেও, দেশের অন্তরাত্মা বা তার সনাতন ধর্মীয় ধারা ও ঐতিহ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সেই ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য বংশপরম্পরায় একই ধারায় সমানে চলেছে। মুদিখানাটি সেই অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত ভারতবর্ষের প্রতীক, যা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন ধারাকে বহন করে চলেছে।
(চ) মুদিখানাটির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
উত্তর: মুদিখানাটি ছিল লেখকের বাসার নিকটে। পঁচিশ বছর পরেও দোকানটির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। জিনিসপত্র আগের মতোই সাজানো ছিল এবং চালে তখনও কেরোসিনের একটি বাতি ঝুলছিল। দোকানের ভিতরে গদিতে বসে এক বৃদ্ধ রামায়ণ পাঠ করতেন, একজন মধ্যবয়স্ক লোক খদ্দের সামলানোর ফাঁকে সেই পাঠ শুনত, এবং কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে আগ্রহের সাথে সেই পাঠ উপভোগ করত।
(ছ) রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের কাহিনিটি লেখো।
উত্তর: পাঠ্যাংশ অনুসারে, রামচন্দ্র কপিসেনার (বানর সেনা) সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই সেতু পার হয়ে তিনি লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছেছিলেন।
৬. রচনাধর্মী উত্তর লেখো
(ক) “সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।” কোন প্রসঙ্গে কে এ উক্তি করেছেন? ট্র্যাডিশন কীভাবে সমানে চলছে তা বুঝিয়ে লেখো।
উত্তর: উক্তিটি ‘ভারতবর্ষ’ গল্পের লেখক এস. ওয়াজেদ আলী করেছেন।
‘ট্র্যাডিশন’ বা ঐতিহ্য বলতে লেখক ভারতবর্ষের মানুষের সহজ-সরল ধর্মপ্রাণতা এবং অধ্যাত্মিক ভাবধারাকে বুঝিয়েছেন। লেখক পঁচিশ বছর পর কলকাতায় ফিরে এসে দেখলেন শহরের বাহ্যিক রূপ আমূল বদলে গেছে। কিন্তু তাঁর বাসার কাছের পুরানো মুদিখানাটি এবং তার ভিতরের দৃশ্য অপরিবর্তিত রয়েছে। ঠিক পঁচিশ বছর আগের মতোই, নতুন প্রজন্মের এক বৃদ্ধ (আগের বৃদ্ধের নাতি) গদিতে বসে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করছেন এবং নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা (বৃদ্ধের নাতি-নাতনি) তন্ময় হয়ে তা শুনছে। এই দৃশ্য দেখে লেখক উপলব্ধি করেন যে, বাইরের পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতির ধারা বা ট্র্যাডিশন বংশপরম্পরায় একই ভাবে সমানে চলেছে।
(খ) “বুড়ো কী পড়ছে তা জানবার জন্য আমার কৌতূহল হল।”-এখানে কার কৌতূহল হল? কৌতূহলের কারণ বিশদ ভাবে আলোচনা করো।
উত্তর: এখানে লেখক এস. ওয়াজেদ আলীর কৌতূহল হল।
লেখকের কৌতূহলের কারণ হল, তিনি যখন দশ-এগারো বছর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন, তখন দেখতেন তাঁর বাসার কাছের মুদিখানায় এক বৃদ্ধ গদিতে বসে সাপ-খেলানো সুরে কী একটা বই পড়তেন। সেই পাঠ শোনার জন্য একটি মাঝারি বয়সের লোক, একটি ছেলে ও দুটি মেয়ে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে বসে থাকত। তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হত তারা বিষয়টি খুব উপভোগ করছে। এই আগ্রহ এবং উপভোগের দৃশ্য দেখেই শিশু লেখকের মনে বৃদ্ধ কী পড়ছেন তা জানার জন্য বিশেষ কৌতূহল জেগেছিল।
(গ) পঁচিশ বছর পূর্বে এবং পরে লেখকের দেখা কলকাতার বিস্তারিত বর্ণনা দাও।
উত্তর:
* পঁচিশ বছর পূর্বে: পঁচিশ বছর পূর্বে লেখক যখন কলকাতায় আসেন, তখন শহর আজকের মতো এত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না। তখন বড় বড় ম্যানশনের বদলে সাধারণ ঘর-বাড়ি ছিল। রাস্তায় বড় মোটরের বদলে দু-চারটে রিকশা আর ঘোড়ার গাড়ি চলত। এবং রাতে রাস্তার ধারে ইলেকট্রিক আলোর বদলে মিটমিট করে গ্যাসের বাতি জ্বলত।
* পঁচিশ বছর পরে: পঁচিশ বছর পর লেখক ফিরে এসে দেখলেন কলকাতার নাগরিক জীবনের বহিরঙ্গে প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। আগেকার সাধারণ ঘরের জায়গায় এখন বড় বড় ম্যানশন (mansion) মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার রিকশা ও ঘোড়ার গাড়ির বদলে এখন বড় বড় মোটর অনবরত যাওয়া-আসা করছে। আর গ্যাসের বাতির বদলে ইলেকট্রিক আলোয় রাস্তাঘাট দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকে।
(ঘ) “প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত ছবি আমার সামনে ফুটে উঠল।”-প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত ছবিটি কী? এর যথাযথ বর্ণনা দাও।
উত্তর: ‘প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত ছবি’ বলতে লেখক ভারতবর্ষের সেই সনাতন ঐতিহ্য বা ট্র্যাডিশনকে বুঝিয়েছেন, যা কালের পরিবর্তনেও বদলায় না।
লেখক পঁচিশ বছর পর কলকাতায় ফিরে যখন দেখলেন শহরের বাইরের খোলস সম্পূর্ণ বদলে গেছে, তখন তিনি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দৈবক্রমে সেই পুরানো মুদিখানাটির সামনে এলেন, তখন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, সেখানে পঁচিশ বছর আগের মতোই এক বৃদ্ধ (আগের বৃদ্ধের নাতি) কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করছেন এবং নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা (বৃদ্ধের নাতি-নাতনি) ঠিক ততটাই আগ্রহ নিয়ে সেই পাঠ শুনছে। এই দৃশ্য দেখে লেখকের দিব্যচক্ষু লাভ হল। তিনি বুঝলেন, এই হল ভারতবর্ষের আসল রূপ—যেখানে বাইরের পরিবর্তন যাই হোক না কেন, ভিতরের অধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতির ধারা বংশপরম্পরায় একই ভাবে প্রবাহিত হয়।
(ঙ) ‘ভারতবর্ষ’ পাঠটি অনুসরণে বৃদ্ধটির পরিচয় দাও এবং তাঁর রামায়ণ পাঠের দৃশ্যটি বর্ণনা করো।
উত্তর:
* বৃদ্ধটির পরিচয়: পাঠে লেখক যে বৃদ্ধটির সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি ছিলেন প্রথম বৃদ্ধের (যাকে লেখক পঁচিশ বছর আগে দেখেছিলেন) পৌত্র বা নাতি। পঁচিশ বছর আগে যে ছেলেটিকে লেখক পাঠ শুনতে দেখতেন, সেই ছেলেটিই বড় হয়ে এই বৃদ্ধের পুত্র হয়েছে।
* রামায়ণ পাঠের দৃশ্য: পঁচিশ বছর পর লেখক মুদিখানায় যে দৃশ্য দেখেছিলেন, তা প্রথমবার দেখার মতোই। বৃদ্ধটি গদির উপর বসে একটি মোটা কৃত্তিবাসের রামায়ণ নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে পড়ছিলেন। তাঁর পাঠের বিষয় ছিল রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন। একটি মধ্যবয়স্ক লোক (বৃদ্ধের পুত্র) খদ্দের দেখার ফাঁকে ফাঁকে এসে পাঠ শুনছিল। আর বৃদ্ধের পাশে তাঁর নাতি (খালি গায়ে) ও দুই নাতনি বসে আগ্রহের সাথে সেই পাঠ উপভোগ করছিল।
৭. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো
(ক) এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরা কি আর বাড়েনি? আর আপনার মধ্যেও কি কোনো পরিবর্তন হয়নি?
প্রসঙ্গ: উক্তিটি লেখক এস. ওয়াজেদ আলী ‘ভারতবর্ষ’ রচনায় মুদিখানার দ্বিতীয় বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন।
ব্যাখ্যা: পঁচিশ বছর পর লেখক মুদিখানায় ফিরে এসে যখন দেখলেন যে, ঠিক পঁচিশ বছর আগের মতোই এক বৃদ্ধ রামায়ণ পড়ছেন এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তা শুনছে, তখন তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। তাঁর মনে হয়েছিল যেন কোনো মায়ামন্ত্রে অতীত ফিরে এসেছে। তাই তিনি অবাক হয়ে বৃদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, এই পঁচিশ বছরেও কি এই ছেলেমেয়েরা বড় হয়নি বা বৃদ্ধের নিজের কোনো পরিবর্তন হয়নি?
(খ) আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছি।
প্রসঙ্গ: উক্তিটি ‘ভারতবর্ষ’ রচনার লেখক এস. ওয়াজেদ আলীর স্বগতোক্তি।
ব্যাখ্যা: পঁচিশ বছর পর কলকাতায় ফিরে লেখক দেখলেন শহরের চেহারায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। এই বদল দেখে তিনি যখন ভাবছিলেন যে কালের প্রভাবে পরিবর্তন ঘটবেই, তা অবশ্যম্ভাবী, ঠিক সেই সময়েই তাঁর চোখ পড়েছিল অপরিবর্তিত সেই পুরানো মুদিখানাটির উপর। এই বৈপরীত্য তুলে ধরতেই লেখক উক্তিটি করেছেন।
(গ) কোনো মায়ামন্ত্র বলে সেই সুদুর অতীত আবার ফিরে এলো নাকি!
প্রসঙ্গ: উক্তিটি ‘ভারতবর্ষ’ রচনার লেখক এস. ওয়াজেদ আলীর স্বগতোক্তি।
ব্যাখ্যা: পঁচিশ বছর পর লেখক যখন সেই মুদিখানার সামনে এলেন, তখন ভিতরকার দৃশ্য দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, ঠিক পঁচিশ বছর আগের মতোই এক বৃদ্ধ রামায়ণ পাঠ করছেন এবং ছোট ছেলেমেয়েরা তা শুনছে। এই দৃশ্য এতই অবিকল ছিল যে, লেখকের মনে হয়েছিল যেন কোনো জাদুবলে সুদূর অতীতকালই বর্তমানে ফিরে এসেছে।
(ঘ) আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে।
প্রসঙ্গ: উক্তিটি ‘ভারতবর্ষ’ রচনার লেখক এস. ওয়াজেদ আলীর।
ব্যাখ্যা: পঁচিশ বছর পর লেখক যখন দৈবক্রমে সেই পুরানো মুদিখানাটির সামনে এলেন, তখন তিনি ভিতরের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, পঁচিশ বছর আগে যেমনটি দেখেছিলেন, ঠিক তেমনই একজন বৃদ্ধ গদিতে বসে রামায়ণ পড়ছেন, একজন মধ্যবয়স্ক লোক খদ্দের সামলাচ্ছে আর পাঠ শুনছে, এবং ঠিক আগের মতোই ছেলেমেয়েরা আগ্রহের সাথে সেই পাঠ শুনছে। এই অপরিবর্তিত দৃশ্য দেখেই তিনি স্তম্ভিত হয়েছিলেন।
(ঙ) পরিবর্তনের কত স্রোত আমার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল।
প্রসঙ্গ: উক্তিটি ‘ভারতবর্ষ’ রচনার লেখক এস. ওয়াজেদ আলীর স্বগতোক্তি।
ব্যাখ্যা: পঁচিশ বছর আগেকার মুদিখানার সেই শান্ত জীবনের ছবিটি লেখকের মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরে লেখকের নিজের জীবনেও বহু পরিবর্তন এসেছে, তিনি দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন। নিজের জীবনের এই বিপুল পরিবর্তনের কথা বোঝাতেই লেখক উক্তিটি করেছেন।
৮. তাৎপর্য লেখো
(ক) তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে গেলুম।
তাৎপর্য: পঁচিশ বছর আগেকার সেই মুদিখানার স্মৃতি লেখকের মন থেকে মুছে গিয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ে লেখকের নিজের জীবনেও বহু পরিবর্তন এসেছে। লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে, দৈনন্দিন জীবনে আমরা এরকম কত শত জিনিস দেখি এবং সময়ের সাথে সাথে তা ভুলে যাই; সেই বৃদ্ধ ও তার সন্তান-সন্ততিদের স্মৃতিও লেখকের কাছে তেমনই এক বিস্মৃত ঘটনা ছিল।
(খ) মনে হলো আমি দিব্যচক্ষু পেয়েছি।
তাৎপর্য: পঁচিশ বছর পর মুদিখানার অপরিবর্তিত দৃশ্য এবং বৃদ্ধের কথা [cite: 33-37] শোনার পর লেখকের এক নতুন উপলব্ধি হল। [cite_start]তিনি বুঝতে পারলেন, ভারতবর্ষের বাইরের রূপ বদলালেও তার সনাতন ঐতিহ্য বা ‘ট্র্যাডিশন’ বদলায়নি। এই গভীর সত্যটি উপলব্ধি করাকেই লেখক ‘দিব্যচক্ষু’ বা অলৌকিক দৃষ্টি লাভ বলে মনে করেছেন।
(গ) এ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, আমার ঠাকুরদা বটতলায় এটি কিনে ছিলেন।
তাৎপর্য: বৃদ্ধের এই উক্তিটি গল্পের মূল ভাবকে ধারণ করে। এটি প্রমাণ করে যে, এই রামায়ণ পাঠ কোনো সাময়িক ব্যাপার নয়, বরং এটি বংশপরম্পরায় চলে আসা এক ঐতিহ্য। বৃদ্ধের ঠাকুরদা এই বইটি কিনেছিলেন, তারপর তাঁর পিতা (লেখকের দেখা প্রথম বৃদ্ধ) এটি পড়তেন, এবং এখন তিনি (পৌত্র) তাঁর নাতি-নাতনিদের তা পড়ে শোনাচ্ছেন। ‘বটতলা’ স্থানটিও বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতীক।
(ঘ) বোধহয় সেই পঁচিশ বছর আগের সেই বাতিটি।
তাৎপর্য: লেখক পঁচিশ বছর পর মুদিখানাটিতে ফিরে এসে যখন দেখলেন চালে এখনও একটি কেরোসিনের বাতি ঝুলছে, তখন তিনি এই মন্তব্যটি করেন। এই বাতিটি হল অপরিবর্তনীয়তার প্রতীক। এটি বাইরের ইলেকট্রিক আলোর ঝলকানির বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা ভারতবর্ষের সেই সনাতন ঐতিহ্যকে সূচিত করে, যা পঁচিশ বছরেও বদলায়নি।
৯. পাঠ-নির্ভর ব্যাকরণ
(ক) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো:
* আপাদমস্তক: পা হইতে মাথা পর্যন্ত (অব্যয়ীভাব সমাস)
* বিপুলকায়: বিপুল কায়া যার (বহুব্রীহি সমাস)
* শ্মশ্রুগুম্ফ: শ্মশ্রু ও গুম্ফ (দ্বন্দ্ব সমাস)
* ঘরবাড়ি: ঘর ও বাড়ি (দ্বন্দ্ব সমাস)
* লঙ্কাদ্বীপ: লঙ্কা নামক দ্বীপ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস)
* মহাশয়: মহান যে আশয় (কর্মধারয় সমাস)
* ঠাকুরদাদা: ঠাকুরের (পিতার) দাদা (সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস)
* বটতলা: বটের তল (সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস)
* নিখুঁত: নাই খুঁত যার (নঞ বহুব্রীহি সমাস)
* মায়ামন্ত্র: মায়া রূপ মন্ত্র (রূপক কর্মধারয় সমাস)
* স্বামীপুত্র: স্বামী ও পুত্র (দ্বন্দ্ব সমাস)
(খ) পদান্তর করো:
* টাক: টেকো (বিশেষণ)
* উৎসাহ: উৎসাহী (বিশেষণ)
* পরিবর্তন: পরিবর্তিত (বিশেষণ)
* ত্যাগ: ত্যক্ত (বিশেষণ) / ত্যাজ্য (বিশেষণ)
* বৃদ্ধ: বার্ধক্য (বিশেষ্য)
* স্বর্গ: স্বর্গীয় (বিশেষণ)
* বিস্ময়: বিস্মিত (বিশেষণ)
* গম্ভীর: গাম্ভীর্য (বিশেষ্য)
(গ) বাক্য পরিবর্তন করো:
* ওর বয়স আপনার মতোই হবে (অস্ত্যর্থক)
উত্তর: ওর বয়স আপনার চেয়ে কম হবে না (নাস্ত্যর্থক)
* সে অনেক দিনের কথা (অস্ত্যর্থক)
উত্তর: সে খুব অল্প দিনের কথা নয় (নাস্ত্যর্থক)
(ঘ) উক্তি কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর: উক্তি দু’ প্রকার— (১) প্রত্যক্ষ উক্তি এবং (২) পরোক্ষ উক্তি।
(ঙ) উক্তি পরিবর্তন করো: (উত্তরগুলি পাঠ্যবইতেই দেওয়া আছে)
(১) প্রত্যক্ষ উক্তি- মালা আমাকে বলল, “এখন বিরক্ত করিস না”।
পরোক্ষ উক্তি – মালা আমাকে বলল যে আমি যেন এখন তাকে বিরক্ত না করি।
(২) প্রত্যক্ষ উক্তি-লেখক বললেন, “পঁচিশ বছর পূর্বে আমি কলকাতায় এসেছিলুম”।
পরোক্ষ উক্তি – লেখক বললেন যে তিনি পঁচিশ বছর পূর্বে কলকাতায় এসেছিলেন।
(৩) প্রত্যক্ষ উক্তি – লেখক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার মধ্যে কি কোনো পরিবর্তন হয়নি”?
পরোক্ষ উক্তি – লেখক বৃদ্ধের কাছে জানতে চাইলেন যে তাঁর মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা।
(৪) প্রত্যক্ষ উক্তি- গুরু শিষ্যকে বললেন, “তুমি এখন বাড়ি যাও”।
পরোক্ষ উক্তি – গুরু শিষ্যকে এখন বাড়িতে যেতে নির্দেশ দিলেন।
(৫) প্রত্যক্ষ উক্তি – রাম বলল, “আজ আমার যাওয়া হবে না।”
পরোক্ষ উক্তি- রাম জানাল যে সে আজ যেতে পারবে না।