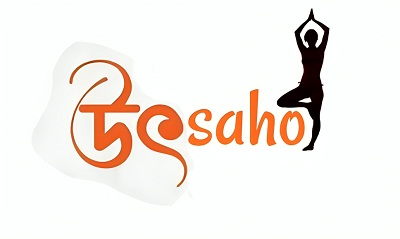মনসামঙ্গল’ ,Chapter- 5, Class-9, SEBA
‘মনসামঙ্গল’ ,Chapter- 5, Class-9, SEBA
প্রশ্নাবলি (সমাধান)
১. শূন্যস্থান পূরণ করো:
ক. সপ্তডিঙা মধুকর চারিদিকে জল।
খ. শ্রাবণের অবিশ্রাম মনসামঙ্গল।
গ. এখনো বুকের দ্বিজ বংশীদাস কহে।
ঘ. কুপিলম্পে রাতকানা নিরক্ষরা বুড়ি।
২. ‘মনসামঙ্গল’ কবিতার বিশেষ্য পদগুলো বাছাই করে সাজিয়ে লেখো।
কবিতাটি থেকে পাওয়া বিশেষ্য পদগুলো হলো:
মধুকর, সপ্তডিঙা, জল, শ্রাবণ, মনসামঙ্গল, পাট, ডোবা, ফণা, কাঁথা-কানি, বেহুলা, যন্ত্রণা, কালসন্ধ্যা, গান, সায়ের, ঝিয়ারি, ভাসান, নিছনি, চম্পকনগর, শিকা, ঘর, ভিতর, কুপিলম্প, রাত, বুড়ি, লখা, মরণ, জাল, ছেলে, মা, মনসা, অঙ্গ, গাঙ, গন্ধ, শ্রাবণী, দিগম্বরা, বাতাস, বুক, দ্বিজ বংশীদাস, কালীদহ, ডহর, গহন, টান।
৩. ‘মনসামঙ্গল’ কবিতার বিশেষণ পদগুলো বাছাই করে লেখো।
কবিতাটি থেকে পাওয়া বিশেষণ পদগুলো হলো:
নিরক্ষরা, অবিশ্রাম, পচা, এঁদো, বিষধর, ছেঁড়া, হু হু-করা, আসা, অনন্ত, সাতনরী, রাতকানা, টানা, সর্বাঙ্গ, গর্ভিণী, দখিনা, ঘোর লাগা, গহনের।
৪. পদ পরিবর্তন করো।
* জল (বিশেষ্য) – জলীয় (বিশেষণ)
* বিষ (বিশেষ্য) – বিষাক্ত (বিশেষণ) (কবিতায় ‘বিষধর’ শব্দটি আছে)
* যন্ত্রণা (বিশেষ্য) – যন্ত্রণাদায়ক (বিশেষণ)
* গান (বিশেষ্য) – গেয় (বিশেষণ)
* ঘর (বিশেষ্য) – ঘরোয়া (বিশেষণ)
* জাল (বিশেষ্য) – জালি (বিশেষণ)
* রাত (বিশেষ্য) – রাত্রিকালীন (বিশেষণ)
* গাঙ (বিশেষ্য) – গাঙুড় (বিশেষণ)
* দখিনা (বিশেষণ) – দক্ষিণ (বিশেষ্য)
৫. আঠ-দশটি বাক্যে উত্তর দাও।
ক. ‘মনসামঙ্গল’ কবিতা অবলম্বনে শ্রাবণের রূপসৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।
‘মনসামঙ্গল’ কবিতায় শ্রাবণের রূপ প্রথাগত সৌন্দর্যের নয়, বরং তা এক তীব্র, আদিম ও জীবনঘনিষ্ঠ রূপ। এই শ্রাবণে “চারিদিকে জল” এবং “অবিশ্রাম মনসামঙ্গল” অর্থাৎ মনসামঙ্গলের সুর বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এটি “পচা পাটে এঁদো ডোবা” এবং সাপের ভয়ের (“বিষধর ফণা”) ঋতু। একদিকে যেমন জীবনের ঝুঁকি, অন্যদিকে তেমনই নদীর উর্বরতার গন্ধ (“গাঙের গর্ভিণী সেই গন্ধ”) এই শ্রাবণেই পাওয়া যায়। “শ্রাবণীর দিগম্বরা দখিনা বাতাসে” লাইনটি শ্রাবণের এক বাঁধনছাড়া, আদিম রূপকে তুলে ধরে। সুতরাং, কবির চোখে শ্রাবণ মাস হলো ভয়, ভক্তি, দারিদ্র্যের যন্ত্রণা এবং প্রকৃতির এক উর্বর, রহস্যময় রূপের মিলিত প্রতিচ্ছবি।
খ. ‘বেহুলা-যন্ত্রণার’ পরিচয় দাও।
‘বেহুলা-যন্ত্রণা’ বলতে মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান নারী চরিত্র বেহুলার অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট ও সংগ্রামকে বোঝানো হয়েছে। বেহুলা ছিলেন উজানী নগরের সায়বেনের কন্যা। চাঁদ সদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু দেবী মনসার রোষের কারণে বাসর রাতেই তাঁর স্বামী লখিন্দর সাপের কামড়ে মারা যান। স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য বেহুলা এক অসম্ভব পণ করেন। তিনি মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে কলার ভেলায় চড়ে “অনন্ত ভাসানে” অর্থাৎ এক বিপদসংকুল ও অন্তহীন নদীপথে যাত্রা করেন। এই যাত্রাপথে সমস্ত প্রতিকূলতা সহ্য করে তিনি শেষ পর্যন্ত দেবলোকে পৌঁছান। সেখানে নিজের নৃত্য-গীতের মাধ্যমে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে তিনি স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও নিজের সতীত্বের জোরে এই যে অকল্পনীয় দুঃখবরণ ও সংগ্রাম, তাকেই ‘বেহুলা-যন্ত্রণা’ বলা হয়। কবিতায় এই পৌরাণিক যন্ত্রণাকে “ছেঁড়া কাঁথা-কানি” অর্থাৎ বর্তমানের দারিদ্র্য ও দুঃখের সঙ্গে এক করে দেখানো হয়েছে।
গ. ‘সায়ের ঝিয়ারি’ কে? তাঁর অনন্ত ভাসানে যাত্রার বর্ণনা দাও।
‘সায়ের ঝিয়ারি’ হলেন মনসামঙ্গল কাব্যের নায়িকা বেহুলা। শব্দার্থ অনুসারে, ‘সায়ের’ বলতে বেহুলার পিতা সায়বেনকে এবং ‘ঝিয়ারি’ বলতে কন্যা বা দুহিতাকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং, ‘সায়ের ঝিয়ারি’-এর আক্ষরিক অর্থ হলো ‘সায়বেনের কন্যা’ অর্থাৎ বেহুলা।
তাঁর ‘অনন্ত ভাসানে’ যাত্রার কারণটি অত্যন্ত করুণ। বাসর রাতে স্বামী লখিন্দর সাপের কামড়ে মারা গেলে, বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে একটি ভেলায় চড়ে নদীতে ভেসে পড়েন। তাঁর লক্ষ্য ছিল দেবলোকে পৌঁছে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনা। নদীপথে এই বিপদসংকুল, অন্তহীন যাত্রাই হলো তাঁর ‘অনন্ত ভাসান’। কবিতায় এই যাত্রাকে “ডহরের ঘোর লাগা গহনের টানে” চলা এক অনন্ত যাত্রা বলা হয়েছে, যা শুধু পৌরাণিক কাহিনীতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা বাঙালির জীবনে বয়ে চলা এক চিরন্তন দুঃখ ও সংগ্রামের প্রতীক।
৬. রচনাধর্মী উত্তর লেখো।
ক. ‘মনসামঙ্গল’ কবিতাটির ভাবার্থ লেখো।
শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর ‘মনসামঙ্গল’ কবিতাটি বাংলার লোকপুরাণ ও আধুনিক জীবনচেতনার এক অপূর্ব মিশ্রণ। কবিতাটির কেন্দ্রীয় ভাবটি হলো—পৌরাণিক দুঃখগাথা কেবল অতীতের কাহিনী নয়, তা বর্তমানের জনজীবনেও একইভাবে প্রবহমান।
কবিতার শুরুতেই শ্রাবণ মাসের একটি ছবি ফুটে ওঠে, যেখানে একদিকে অবিরাম মনসামঙ্গলের সুর, অন্যদিকে “পচা পাটে এঁদো ডোবা” ও “বিষধর ফণা”র মতো বাস্তব জীবনের রূঢ় চিত্র। কবি দেখিয়েছেন, বেহুলার পৌরাণিক যন্ত্রণা (“বেহুলা-যন্ত্রণা”) আর বর্তমানের দারিদ্র্য (“ছেঁড়া কাঁtha-কানি”) যেন একই সূত্রে গাঁথা।
দ্বিতীয় স্তবকে, কবি চম্পকনগরের মতো পৌরাণিক স্থানের পাশে “সাতনরী শিকা” বা “কুপিলম্পে” আলোয় বসা এক “নিরক্ষরা বুড়ি”র ছবি আঁকেন। এই বুড়ি লখিন্দরের (“লখার”) জন্য যেমন কাঁদেন, তেমনি “জাল-টানা ছেলে” অর্থাৎ বর্তমানের সন্তানের জন্যও মা মনসার কাছে প্রার্থনা করেন। এর মাধ্যমে কবি অতীত ও বর্তমানের মাতৃহৃদয়ের উদ্বেগকে এক করে দেখান।
শেষ স্তবকে, “গাঙের গর্ভিণী সেই গন্ধ” এবং “শ্রাবণীর দিগম্বরা দখিনা বাতাস” এক আদিম, চিরন্তন প্রকৃতির ছবি তৈরি করে। কবি “দ্বিজ বংশীদাস” -এর কণ্ঠস্বরকে উদ্ধৃত করে বলেন যে, এই কাহিনী এখানে শেষ নয় (“হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কালীদহে…”)। বেহুলার যাত্রা (“সায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে”) আজও শেষ হয়নি। তা বাঙালির জীবনে সংগ্রাম ও যন্ত্রণার এক অন্তহীন ভাসান হয়েই রয়ে গেছে।
খ. ‘সায়ের ঝিয়ারি’ কথার অর্থ কী? তিনি কেন ভাসানে গেলেন? তাঁর এই ভাসান-যাত্রার করুণ বিবরণ বিশদ করো।
‘সায়ের ঝিয়ারি’ কথাটির অর্থ হলো ‘সায়বেনের কন্যা’। ‘সায়ের’ শব্দটি বেহুলার পিতা ‘সায়বেন’ -এর কথ্য রূপ এবং ‘ঝিয়ারি’ শব্দের অর্থ হলো কন্যা বা দুহিতা। মনসামঙ্গল কাব্য অনুসারে, বেহুলা ছিলেন উজানী নগরের সায়বেনের কন্যা। সুতরাং, ‘সায়ের ঝিয়ারি’ বলতে বেহুলাকেই বোঝানো হয়েছে।
বেহুলা ‘ভাসানে’ গিয়েছিলেন তাঁর মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে। চাঁদ সদাগরের পুত্র লখিন্দরের সঙ্গে বিয়ের রাতে দেবী মনসার আদেশে সাপ লখিন্দরকে দংশন করে ও তাঁর মৃত্যু হয়। বেহুলা এই অকাল বৈধব্যকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি স্বামীর মৃতদেহ সৎকার না করে, তা একটি ভেলায় নিয়ে নদীতে ভেসে পড়েন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেবলোকে গিয়ে দেবতাদের তুষ্ট করে স্বামীর পুনর্জীবন লাভ করা।
তাঁর এই ভাসান-যাত্রার বিবরণ অত্যন্ত করুণ। কবিতাটি এই যাত্রাকে “অনন্ত ভাসানে” অর্থাৎ এক অন্তহীন যাত্রা বলে অভিহিত করেছে। এই যাত্রা ছিল “বেহুলা-যন্ত্রণা” বা চরম দুঃখের প্রতীক। সদ্যবিবাহিতা বেহুলাকে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে এক অজানা, বিপদসংকুল নদীপথে পাড়ি দিতে হয়েছিল। তাঁকে একাই প্রকৃতির রোষ এবং সামাজিক লাঞ্ছনার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। ‘টীকা’ অনুসারে, তিনি এই কঠিন যাত্রাপথ অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত দেবলোকে পৌঁছেছিলেন এবং সেখানে নিজের নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে দেবতাদের, বিশেষত শিবকে, সন্তুষ্ট করেন। তাঁর সতীত্বের জোরেই তিনি কেবল স্বামীর প্রাণই নয়, বরং শ্বশুরের হারানো ছয় পুত্র ও চৌদ্দটি ডিঙাও ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। এই করুণ অথচ দৃঢ়তাপূর্ণ যাত্রা বেহুলাকে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সতী ও সংগ্রামী নারী চরিত্রে পরিণত করেছে।
৭. তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
ক. সায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে।
তাৎপর্য: এই চরণটি কবিতার মূল সুরকে ধারণ করে আছে। ‘সায়ের ঝিয়ারি’ অর্থাৎ বেহুলা যেমন তাঁর মৃত স্বামীকে নিয়ে অনন্ত যাত্রায় ভেসে গিয়েছিলেন, কবি সেই পৌরাণিক চিত্রকল্পকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এখানে ‘অনন্ত ভাসান’ শুধু বেহুলার ভেলায় ভেসেই চলা নয়, তা বাঙালি জীবনের দুঃখ, সংগ্রাম ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক চিরন্তন যাত্রার প্রতীক। কবি বোঝাতে চেয়েছেন, বেহুলার সেই যাত্রা আজও শেষ হয়নি; তা আজও বাংলার দরিদ্র, সংগ্রামী মানুষের জীবনে (“ছেঁড়া কাঁtha-কানি”, “জাল-টানা ছেলে”) প্রবহমান।
খ. ছেঁড়া কাঁথা-কানি আর বেহুলা-যন্ত্রণা।
তাৎপর্য: এই চরণে কবি বর্তমানের রূঢ় বাস্তবতাকে পৌরাণিক যন্ত্রণার সঙ্গে একীভূত করেছেন। “ছেঁড়া কাঁথা-কানি” হলো দারিদ্র্য, অভাব ও অবহেলার বাস্তব চিত্র, যা বিশেষত বর্ষার “পচা পাটে এঁদো ডোবা”র পরিবেশে আরও করুণ হয়ে ওঠে। “বেহুলা-যন্ত্রণা” হলো স্বামীহারা এক নারীর অসীম দুঃখ ও সংগ্রামের পৌরাণিক কাহিনী। কবি এই দুটিকে পাশাপাশি বসিয়ে বুঝিয়েছেন যে, পৌরাণিক সেই দুঃখের ভার আর বর্তমানের দারিদ্র্যের যন্ত্রণা本质ত একই। বাংলার সাধারণ মানুষ আজও বেহুলার মতোই যন্ত্রণাময় জীবন অতিবাহিত করে চলেছে।
গ. গাঙের গর্ভিণী সেই গন্ধ ভেসে আসে।
তাৎপর্য: এই চরণটি শ্রাবণ মাসের এক তীব্র, আদিম ও উর্বর রূপকে প্রকাশ করে। “গাঙ” বা নদী হলো বাংলা ও মনসামঙ্গল কাহিনীর প্রাণ। বর্ষায় সেই নদী যখন কূলে কূলে ভরা, তখন মাটির, জলের ও পচনশীল প্রকৃতির যে মিশ্র গন্ধ (“পচা পাটে”) বাতাসে ভাসে, তাকেই কবি “গর্ভিণী” (Pregnant) বলেছেন। এই গন্ধ জীবনের উর্বরতার প্রতীক, যা নতুন সৃষ্টির ইঙ্গিত বহন করে। এই আদিম গন্ধই যেন মনসামঙ্গল কাহিনীর সেই প্রাচীন সময়কে বর্তমানের সঙ্গে জুড়ে দেয়।
ঘ. শ্রাবণীর দিগম্বরা দখিনা বাতাসে।
তাৎপর্য: এখানে শ্রাবণ মাসের দক্ষিণ বাতাসকে “দিগম্বরা” (অর্থাৎ উলঙ্গ বা আবরণহীন) বলে বিশেষায়িত করা হয়েছে। “দিগম্বরা” শব্দটি সাধারণত শিব বা কালীর মতো প্রলয়ঙ্করী ও আদিম সত্তার সঙ্গে যুক্ত। কবি শ্রাবণের বাতাসকে এই রূপ দিয়ে তার বাঁধনহীন, আদিম ও প্রলয়ঙ্করী শক্তিকে বুঝিয়েছেন। এই বাতাসই “গাঙের গর্ভিণী গন্ধ” বয়ে আনে এবং মনসামঙ্গলের ভয় ও ভক্তির পরিবেশকে তীব্রতর করে তোলে। এটি প্রকৃতির সেই রূপ, যা সৃষ্টির পাশাপাশি ধ্বংসেরও ইঙ্গিত দেয়।
ব্যাকরণ: নির্দেশক প্রত্যয় (আলোচনা)
PDF ফাইলের ৫ ও ৬ নং পৃষ্ঠায় [cite: 45-60] বাংলা ব্যাকরণের “নির্দেশক প্রত্যয়” অংশটি আলোচনা করা হয়েছে। এর মূল বিষয়বস্তু নিচে সারসংক্ষেপ করা হলো:
নির্দেশক প্রত্যয় কী?
[cite_start]বিশেষ্য পদের পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ওই পদের নির্দিষ্টতা (definiteness), সংখ্যা, আকার, বা বস্তুর প্রতি বক্তার মনোভাব (আদর, অনাদর) প্রকাশ করে, তাকে নির্দেশক প্রত্যয় বলে।
প্রধান নির্দেশক ও তাদের ব্যবহার:
১. -টা, -টি:
* পূর্ণ বা অখণ্ড বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
* অপ্রাণীবাচক শব্দে সাধারণত বসে।
* -টা: অনাদর বোঝাতে মানুষ বা প্রাণীর সঙ্গে ব্যবহৃত হয় (যেমন- “লোকটা”)।
* -টি: স্নেহ, অনুকম্পা বা আদর বোঝাতে ব্যবহৃত হয় (যেমন- “মানুষটি,” “ছেলেটি”)। এটি বস্তুর হ্রস্ব-ভাব বা ছোট আকার বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়।
* এর উৎপত্তি সংস্কৃত “বৃত্ত” শব্দ থেকে।
২. -খানা, -খানি:
* যেসব বস্তু খণ্ডিত হতে পারে বা যা সমতল ও চ্যাপ্টা বোঝায়, তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় (যেমন- “কাপড়-খানা,” “মুখখানি”)।
* গোলাকার বস্তুর সঙ্গে সাধারণত বসে না (যেমন- “বল-খানা” হয় না)।
* -খানি: হ্রস্বভাব (ছোট) বা আদর বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
* এর উৎপত্তি সংস্কৃত “খণ্ড” শব্দ থেকে।
৩. -গাছা, -গাছি:
* সরু বা দীর্ঘ বস্তুর নামের সঙ্গে প্রযুক্ত হয় (যেমন- “লাঠি-গাছি,” “খড়-গাছা”)।
* -গাছি: হ্রস্বভাব বা আদর বোঝাতে বসে।
* এর উৎপত্তি বাংলা “গাছ” শব্দ থেকে।
৪. -টুকু, -টুকুন:
* পরিমাণে অল্প বা ক্ষুদ্রতা বোঝাতে এবং আদর প্রকাশে ব্যবহৃত হয় (যেমন- “এতটুকু জল,” “দুধটুকু”)।
অন্যান্য ব্যবহার:
* সংখ্যার সঙ্গে: সংখ্যাবাচক শব্দের পরে বসে নির্দিষ্টতা বোঝায় (যেমন- “বই তিন-খানা”), অথবা সংখ্যাবাচক শব্দের আগে বসে অনির্দিষ্ট বা আন্দাজ বোঝায় (যেমন- “খান-চার কাপড়”)।
* পরিমাণের সঙ্গে: পরিমাণবাচক বিশেষণের সঙ্গেও যুক্ত হয় (যেমন- “এতটা জল,” “অনেকখানি সোনা”)।