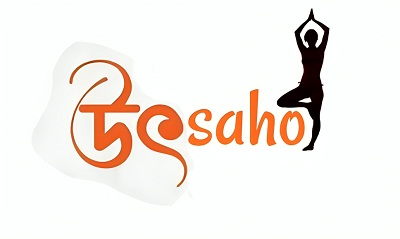ভারত এবং উত্তরপূর্বাঞ্চলের ঐতিহ্য Part -2
ভারত এবং উত্তরপূর্বাঞ্চলের ঐতিহ্য Part -2
২৮। মোগল যুগের ক্ষুদ্রাকার চিত্র-সম্বলিত তিনটি গ্রন্থের নাম লেখো।
উত্তর: মোগল বাদশাহদের জীবনভিত্তিক-রচিত বা অন্যান্য যে গ্রন্থরাজিতে ক্ষুদ্রাকার চিত্রশৈলীর প্রসার দেখা যায়, তার তিনটি উদাহরণ:
* পাদশাহনামা।
* তুতিনামা।
* জাহাঙ্গিরনামা।
* এছাড়াও দাস্তান-এ-আমির, খামসা ইত্যাদি গ্রন্থ সচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল।
২৯। চিত্রকলার ষড়াঙ্গ মানে কী বোঝ?
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে চিত্র অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় যে ছয়টি অঙ্গের চর্চা হয়েছিল, সেগুলিকেই চিত্রকলার ষড়াঙ্গ বলা হয়। এই ষড়াঙ্গ হলো:
* আকৃতি।
* মাপজোখ।
* আবেগ অনুভূতি প্রকাশের কৌশল।
* শৈল্পিক উপস্থাপন।
* সাদৃশ্য জ্ঞান।
* তুলিকা ব্যবহারের নিয়ম।
৩০। ভারতের যোগবিদ্যা বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
উত্তর: যোগবিদ্যা ভারতবর্ষের গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম। এটি শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের এক সচেতন সক্রিয় পদ্ধতি।
* উৎপত্তি: সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই ভারতীয়রা যোগজ্ঞানের অধিকারী ছিল বলে অনুমান করা হয় এবং বৈদিক যুগে এর সর্বাধিক চর্চা হয়েছিল।
* সংহত রূপদান: আনুমানিক খ্রিস্টীয় ২য় শতকে (২০০ খ্রিস্টাব্দে) মহর্ষি পতঞ্জলি ‘যোগসূত্র’ নামক গ্রন্থ সংকলন করে যোগবিদ্যাকে সুসংহত রূপদান করেন।
* অষ্টাঙ্গ যোগ: পতঞ্জলির যোগ পদ্ধতিতে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি নামক ‘অষ্টাঙ্গ’ যোগের বিধান দেওয়া হয়েছে।
* স্বতন্ত্র দর্শন: এটি জীবনযাপনের সম্পূর্ণ প্রণালী হিসেবে এক স্বতন্ত্র দর্শন আকারে রূপদান করে।
* আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি: যোগবিদ্যার ফলপ্রসূ কার্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ২০১৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ ২১ জুন তারিখটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।
৩১। ভারতের স্থাপত্যকলার তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
উত্তর: প্রাচীন ভারতে নির্মিত স্থাপত্যের (প্রধানত মঠ-মন্দির, স্তূপ) তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য:
* তিনটি নির্মাণ শৈলী: মন্দির নির্মাণ শৈলীকে মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়— নাগর, দ্রাবিড়, এবং ওয়েসর শৈলী।
* শিখরের ভিন্নতা: উত্তর ভারতের মন্দিরগুলোর চূড়াশীর্ষ অর্ধবৃত্তাকার হয়। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলোর ঊর্দ্ধাংশ (বিমান) আয়তাকারে ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে যাওয়া ধরনের হয়।
* ভাস্কর্য ও বাস্তুশাস্ত্র: কিছু কিছু মন্দিরে অজস্র দেব-দেবীর মূর্তি সারিবদ্ধভাবে খোদাই করে দেওয়া হত। মন্দিরগুলো মূলত হিন্দু বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে নির্মিত হয়েছিল।
* (অতিরিক্ত হিসেবে মোগল যুগের): সুলতানি ও বাদশাহি যুগে মসজিদ, মহল, স্মৃতিসৌধ এবং মিনারের মতো স্থাপত্য দেখা যায়, যেখানে ফারসি শৈলীর প্রয়োগ ছিল।
৩২। রঙালি বিহুর সাত দিনকে কী কী নামে জানা যায়?
উত্তর: রঙালি বিহুর সাত দিনকে ক্রমে নিম্নলিখিত নামে জানা যায়:
* গরু বিহু।
* মানুষ বিহু।
* গোসাঁই বিহু।
* কুটুম বিহু।
* চেনেহি বিহু।
* মেলা বিহু।
* চেরা বিহু।
* (স্থান ভেদে এই নামগুলির তারতম্য ঘটতে দেখা যায়)।
৩৩। কামরূপী লোকগীত এবং গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের মূল বিষয়বস্তু কী?
উত্তর: এই দুটি লোকগীতের মূল বিষয়বস্তু হলো:
* জীবনের সুখ-দুঃখ।
* দেহের ক্ষণভঙ্গুরতা।
* জীবনে ঈশ্বর চিন্তার গুরুত্ব।
* দেব-দেবীর প্রশস্তি আদি প্রকাশমূলক গীত।
* এছাড়াও, গোয়ালপাড়িয়া লোকগীত স্থানীয় কিংবদন্তি তথা হাতি-ধরা ও পোষ মানানো বিষয় নিয়ে রচিত।
৩৪। অসমের প্রাচীন নাম কামরূপ এবং প্রাগজ্যোতিষের উল্লেখ আছে এমন তিনটি গ্রন্থের নাম লেখো।
উত্তর: অসমের প্রাচীন নাম কামরূপ এবং প্রাগজ্যোতিষের উল্লেখ আছে এমন তিনটি গ্রন্থ হলো:
* রামায়ণ।
* মহাভারত।
* বিষ্ণুপুরাণ।
* এছাড়াও কালিকাপুরাণ, যোগিনীতন্ত্র, হিউয়েনসাঙের টীকা, অসমের প্রাচীন রাজবংশীয় লিপি প্রভৃতিতে এই দুটি নাম পাওয়া যায়। ভারতের ঐতিহ্য টিকা
—
১। প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য শিল্প:
প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য শিল্প সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই বিকশিত। ভারতীয় শিল্পীরা পোড়ামাটি, পাথর, ব্রোঞ্জ, তামা, রূপা, সোনা প্রভৃতি ব্যবহার করে মূর্তি নির্মাণে নিজস্ব শৈলী প্রয়োগ করতেন। মূর্তিগুলিতে মানসিক ভাব যেমন সুখ, ক্রোধ ইত্যাদির সূক্ষ্ম প্রকাশ ঘটত। গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর, দেবদেবী, যক্ষ-যক্ষিণী প্রভৃতি বিষয় ফুটে উঠত। অশোকস্তম্ভের পশু মূর্তি ছিল অসাধারণ নিদর্শন। ভাস্কর্য শিল্প গান্ধার, মথুরা ও অমরাবতী—এই তিন শৈলীতে বিকশিত হয়, যেখানে গ্রিক-রোমান প্রভাব এবং দেশীয় কলার সংমিশ্রণ ঘটে।
—
২। ভারতীয় চিত্রকলা:
ভারতের চিত্রকলার ইতিহাস দুই ভাগে বিভক্ত—দেয়ালচিত্র ও ক্ষুদ্রচিত্র। অজন্তা, বাঘ, চিত্তনায়াচল প্রভৃতি গুহার দেয়ালে ধর্মীয় বিষয়ক চিত্র অঙ্কিত হয়। প্রাকৃতিক রঙ যেমন ভুসাকালি, সিঁদূর, হরীতকীর রস ব্যবহার করা হতো। মধ্যযুগে তালপাতা, পাট বা কাপড়ে ক্ষুদ্রচিত্র আঁকা হতো। সুলতানি আমলে পারস্য প্রভাব দেখা যায়। মোগল যুগে আকবর, জাহাঙ্গির ও সাজাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রকলার উন্নতি হয়। এই যুগে সম্রাটদের জীবন, যুদ্ধ, শিকার ও প্রকৃতিচিত্রে শিল্পীরা নিপুণতা প্রদর্শন করেন।
—
৩। ভারতের সংগীত ও নৃত্যকলার ঐতিহ্য:
ভারতের সংগীতের সূচনা সামবেদ যুগে, যজ্ঞে দেবতার উদ্দেশ্যে গীত পাঠ থেকে। ভরত মুনির ‘নাট্যশাস্ত্র’ সংগীত ও নৃত্যের প্রথম গ্রন্থ। ধ্রুপদি সংগীত গুরু-শিষ্য পরম্পরায় আজও বিদ্যমান। বাঁশি, তবলা, সেতার, বীণা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো। সংগীতের পাশাপাশি নৃত্যেরও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। ভারত সরকার স্বীকৃত আটটি ধ্রুপদি নৃত্য হল কথাকলি, মোহিনীআট্টম, ভরতনাট্যম, কুচিপুড়ি, ওড়িশি, কথক, সত্রীয়া ও মণিপুরি। এই সংগীত ও নৃত্যকলার ঐতিহ্য আজও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ।
—
৪। অসমের ভাস্কর্য শিল্প:
অসমে মন্দিরের দেয়ালে খোদাই করা ও পূর্ণাঙ্গ ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্য পাওয়া যায়। শিলা ছাড়াও হাতির দাঁত, ধাতু ও কাঠ ব্যবহার হতো। তেজপুর, বামুনি পাহাড়, মদন কামদেব, আমবাড়ি প্রভৃতি স্থানে নিদর্শন মিলেছে। দ-পর্বতীয়ার তোরণে গঙ্গা-যমুনার মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যা গুপ্ত যুগের প্রভাব নির্দেশ করে। মদন কামদেব মন্দিরের মৈথুন ও দেবমূর্তিগুলি তান্ত্রিক রীতিতে নির্মিত বলে মনে করা হয়। এই ভাস্কর্যগুলো শিল্পকলায় সূক্ষ্ম রুচি ও ভাবপ্রকাশের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।
—
৫। অসমের স্থাপত্য শিল্প:
অসমের স্থাপত্যে আহোম ও কোচ রাজাদের প্রভাব ছিল। রাজকীয় স্থাপনার মধ্যে রংঘর, কারেংঘর ও তলাতল ঘর প্রধান, যেগুলো শিবসাগরে অবস্থিত। রংঘরটি বিহু উৎসব দেখার অট্টালিকা হিসেবে বিখ্যাত। মন্দির স্থাপত্যে কামাখ্যা, উমানন্দ, শিবদোল, জয়দোল, নবগ্রহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নাগর ও ওয়েসর শৈলীর প্রভাব দেখা যায়। নির্মাণে ইট ও পাথর ব্যবহৃত হতো এবং চাউল, ডিম, মাছ দিয়ে করাল নামক গাঁথুনি তৈরি করা হতো। আহোম আমলে স্থাপত্য নিয়ন্ত্রণে চাংরুং ফুকন নামে কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলেন।
—
৬। অসমের বৈষ্ণব সাহিত্য:
পঞ্চদশ শতকে শংকরদেব ও মাধবদেবের নেতৃত্বে অসমে নব বৈষ্ণব আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনে সাহিত্যে নবজাগরণ ঘটে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণভিত্তিক কীর্তন, নামঘোষা ও বরগীত রচিত হয়। নাট্যরচনায় শংকরদেবের পত্নীপ্রসাদ, কালীয়দমন, পারিজাত হরণ ও মাধবদেবের দধিমথন উল্লেখযোগ্য। শংকরদেবের নাট্যচিহ্নযাত্রা বিশ্বনাট্যের প্রাচীন নিদর্শন। ভট্টদেব গদ্যরচনার সূচনা করেন। আজও নামঘর ও সত্রে এই সাহিত্য ভাওনা আকারে পরিবেশিত হয়, যা অসমীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে।
—
৭। অসমের লোকসংগীত:
অসমের সমাজজীবনে নানা উপলক্ষ্যে ভিন্নধর্মী লোকগীত গাওয়া হয়। শিশুকে ঘুম পাড়াতে নিচুকণি গীত গাওয়া হয়, বিয়ের নানা পর্যায়ে বিয়া-নাম পরিবেশিত হয়। বসন্তে রোগ নিবারণের জন্য আইনাম, ধাইনাম প্রচলিত। কামরূপী ও গোয়ালপাড়িয়া লোকগীত জীবনের সুখদুঃখ, ঈশ্বরচিন্তা ও প্রকৃতি নিয়ে রচিত। টোকারি গীত, দরঙের চিয়াগীত ও গরখিয়া গীতও জনপ্রিয়। সুফি সাধক আজান পীরের জিকির ও জারি গান ধর্মীয় সংহতির প্রতীক। এই ঐতিহ্যে প্রতিমা পাণ্ডে বরুয়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।
—
৮। অসমের ধর্মীয় সংহতি:
অসমে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ প্রভৃতি ধর্মের সহাবস্থান এক অনন্য উদাহরণ। হিন্দুধর্মে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও সৌর পন্থা প্রচলিত। কামাখ্যা মন্দির শাক্তপীঠ হিসেবে বিখ্যাত, আবার বৈষ্ণব আন্দোলনে শংকরদেব বহু মানুষকে একত্রিত করেন। ইসলাম ধর্ম ত্রয়োদশ শতকে আসে, হাজোর পোয়ামক্কা তীর্থস্থান ও আজান পীরের জিকির-জারি সমাজে প্রভাব ফেলে। শিখ সৈন্যদের বংশধররাও অসমীয় সংস্কৃতিতে মিশে যায়। আহোম রাজারা সর্বধর্ম সমন্বয়ের নীতি গ্রহণ করে সংহত সমাজ গড়ে তুলেছিলেন।
—
৯। অসমের বুরঞ্জি সাহিত্য:
আহোম রাজাদের আমলে রচিত বুরঞ্জি সাহিত্য অসমের ইতিহাসচর্চার মূল উৎস। ‘বুরঞ্জি’ মানে রাজকীয় ঘটনাবলির বিবরণ। প্রাথমিকভাবে এগুলি আহোমদের টাই ভাষায় লেখা হলেও ষোড়শ শতক থেকে অসমীয় ভাষায় রচিত হয়। এই সাহিত্য আহোম রাজবংশের যুদ্ধ, প্রশাসন, কূটনীতি ও সামাজিক ঘটনাবলি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করে। দেওধাই, তুংখুঙিয়া, কছারি, জয়ন্তীয়া, ত্রিপুরা ও পদ্য বুরঞ্জি উল্লেখযোগ্য। চাংরুং ফুকনের নির্মাণকর্মসংক্রান্ত বুরঞ্জিও ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। বুরঞ্জিগুলি আজও ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে মূল্যবান।
—
১০। বিহু উৎসব:
অসমের সর্বাধিক জনপ্রিয় উৎসব বিহু বছরে তিনবার পালিত হয়—রঙালি, কঙালি ও ভোগালি। রঙালি বিহু বসন্তের আগমনে অনুষ্ঠিত হয়, এতে গরু বিহু ও মানুষ বিহু দুই অংশ থাকে। এই সময়ে হুঁচরি, জেং বিহু ও মুকলি বিহু নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হয়। কঙালি বিহু আশ্বিন মাসে, উপবাস ও তুলসি তলায় দীপ জ্বালিয়ে পালন করা হয়। ভোগালি বিহু মাঘ মাসে খাদ্যসমৃদ্ধির আনন্দে পালিত হয়; মেজি জ্বালানো ও ভেলাঘর নির্মাণ এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বিহু উৎসবে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়।