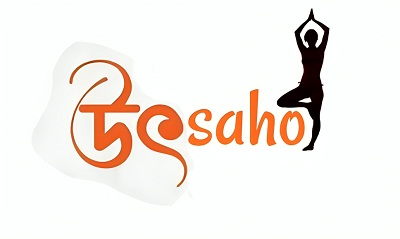সংস্কৃতি এবং আমাদের জীবন,পাঠ – ১৪
পাঠ – ১৪: সংস্কৃতি এবং আমাদের জীবন
ক – পাঠভিত্তিক ক্রিয়াকলাপ
১। পাঠটি স্পষ্ট উচ্চারণে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে উত্তর বলো ও লেখো।
(ক) রূপকোঁয়র জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার মতে সংস্কৃতি কী?
* উত্তর: রূপকোঁয়র জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার মতে সংস্কৃতি হলো— “যে কথা, যে কাজ বা চিন্তা মানুষকে বর্বর প্রকৃতি থেকে তুলে নিয়ে দিব্য প্রকৃতি দেয়, এই পৃথিবীটি সুন্দর করে মানুষকে জীবনের সম্পূর্ণ আনন্দ লাভের রাস্তা দেখায়- মানুষের সেই কথা, সেই চিন্তা বা সেই কাজই হচ্ছে সংস্কৃতি।”
(খ) ভারতীয় জাতি কীভাবে গড়ে উঠেছে?
* উত্তর: নানা জাতির সম্মিলন ও সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় জাতি গড়ে উঠেছে। এই জাতিগুলির ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য মূলত পৃথক ছিল, কিন্তু তারা সকলেই এক বিরাট সমন্বয়ে বিলীন হয়ে এক নবসৃষ্ট জাতিতে নিজ সার্থকতা লাভ করেছে।
(গ) ভারতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো কথা কী?
* উত্তর: ভারতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো কথা হলো পরমত সহিষ্ণুতা। এর অর্থ হলো, বিভিন্ন ধর্মমত বা বিচার একই সত্যে পৌঁছানোর বিভিন্ন পথ মাত্র— এই বোধকে জাতির মজ্জায় প্রবিষ্ট করা এবং আপাত বিরোধী মতবাদের মধ্যকার ঐক্য বা সামঞ্জস্যের চেষ্টা করা।
(ঘ) ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় বড়ো কথা কী?
* উত্তর: ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় বড়ো কথা হচ্ছে এর তত্ত্বানুসন্ধিৎসা। অর্থাৎ, বিচারের পথে বা অনুভূতির পথে, দৃশ্যমান জীবনের অন্তরালে অবস্থিত শাশ্বত সত্য বা সত্তার অনুসন্ধান এবং জীবনে তার উপলব্ধি।
(ঙ) ভারতীয় সংস্কৃতির তৃতীয় কথাটি কী?
* উত্তর: ভারতীয় সংস্কৃতির তৃতীয় কথাটি হলো অহিংসা। এই অহিংসা কেবল প্রাণী হত্যা থেকে বিরতি নয়, এর পিছনে আছে ‘করুণা’ (সমস্ত প্রাণীর সম্বন্ধে দার্শনিকের চোখে দেখা দরদ) এবং ‘মৈত্রী’ (সকলকে মিত্রভাবে দেখে তাদের মঙ্গল করার চেষ্টা)।
(চ) ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পর ভারতীয় সংস্কৃতিতে কী কী বৈশিষ্ট্যের সংযোজন হয়?
* উত্তর: আধুনিক ইউরোপের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পর মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে স্থূল-সূক্ষ্ম নানা ভাবধারা এসে মিশেছে, যেমন— নানা ধরনের খ্রিস্টান মত ও সাধনা, জনসেবা, নানা নতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আর সাহিত্যিক প্রকাশ, নানা নব-নব শিল্প-সৃষ্টি।
(ছ) আমাদের আদর্শ কেমন হওয়া চাই?
* উত্তর: আমাদের আদর্শ হওয়া চাই এক মৌলিক বিশ্ব-সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অনুসারে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য, ভাষা প্রভৃতির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে বহুরূপে বিরাজ করবে এবং পৃথিবীর তাবৎ মানব-জাতিকে তাদের সহজ সাধারণ মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত করে এক করে তুলবে।
২। পাঠের কঠিন শব্দের অর্থ শব্দ-সম্ভার বা অভিধান থেকে শিখে নাও।
* উত্তর: (এটি একটি নির্দেশনামূলক কাজ। শিক্ষার্থীরা পাঠের কঠিন শব্দগুলির অর্থ অভিধান থেকে শিখে নেবে।)
৩। শূন্যস্থান পূর্ণ করো।
* উত্তর:
প্রকৃতিতে এই পার্থিব সভ্যতা অন্য পাঁচটি দেশের পার্থিব সভ্যতার সমপর্যায়েরই বস্তু, ভারতের বস্তু, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা ও নানা হস্তশিল্প, ভারতের দর্শন আর ধর্ম, ভারতের সাহিত্য – এ-সব তো আছে; কিন্তু এর প্রাণ কোথায়?
৪। প্রসঙ্গের সঙ্গে সংগতি রেখে ব্যাখ্যা করো।
(ক) ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যুগে যুগে নতুন ভাব-পরম্পরা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে, সমর্থও হয়েছে,
* উত্তর:
প্রসঙ্গ: এই উক্তিটি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিরন্তন বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সমন্বয় এবং বিবর্তনের ক্ষমতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।
ব্যাখ্যা: ভারতীয় সংস্কৃতি শুরু থেকেই একটি সমন্বয়ী সংস্কৃতি। এর ভিত্তি বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ও তাদের ঐতিহ্যের বিলীন হয়ে যাওয়া। তাই যুগে যুগে যখনই কোনো নতুন ভাবধারা বা সংস্কৃতি (যেমন— ইসলামি সংস্কৃতি, সুফি মতবাদ, বা আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতি) ভারতে প্রবেশ করেছে, তখনই এই সংস্কৃতি সেগুলিকে গ্রহণ ও আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছে এবং সফলও হয়েছে। এই ক্ষমতা থাকার ফলেই ভারতীয় সংস্কৃতি এত বৈচিত্র্যময় এবং এত দীর্ঘকাল ধরে জীবন্ত ও গতিশীল।
(খ) ঝড়ের পরে মৃদু সমীরণের মতো সুফি মতবাদের আর ভারতীয় ভক্তিবাদের সমীকরণই হচ্ছে ভারতে ইসলামি আর হিন্দু সংস্কৃতির সংযোগ বা সংস্পর্শের মুখ্য কথা।
* উত্তর:
প্রসঙ্গ: এই উক্তিটি ভারতে ইসলামি সংস্কৃতির আবির্ভাবের পর হিন্দু ও ইসলামি সংস্কৃতির মধ্যেকার মিলন বা সমন্বয়ের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করছে।
ব্যাখ্যা: ইসলামি সংস্কৃতি যখন ভারতে আসে, তখন প্রাথমিকভাবে তা উগ্র পরমত-অসহিষ্ণুতার সঙ্গে ভারতীয় নম্র পরমত-সহিষ্ণুতার এক সংঘাতের সৃষ্টি করে, যেখানে বিরোধ ছিল প্রধান। এই সংঘাতকে লেখক ‘ঝড়’-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু এই ঝড়ের পরেই আসে ‘মৃদু সমীরণ’ বা শান্ত বাতাস। ইসলাম ধর্মের সুফি মতবাদ (যা প্রেম ও অনুভূতির মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা শেখায়) এবং হিন্দু ধর্মের ভক্তিবাদের (যা ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদ রূপে উপাসনা করতে শেখায়) মধ্যে এক গভীর সাদৃশ্য ছিল। এই দুই মতের মিলনেই (সমীকরণ) ভারতে এমন এক মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতি জন্ম নেয় যা সংঘর্ষকে ছাপিয়ে মিলন ও ভালোবাসার পথ দেখায়। এই মিলনই দুই সংস্কৃতির সংস্পর্শের মুখ্য বা প্রধান কথা।
৫। বুঝিয়ে লেখো।
(ক) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কৃতির প্রভেদগুলো বিশ্লেষণ করো।
* উত্তর:
সংস্কৃতি হলো একটি জাতির জীবনের চালিকা শক্তি। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সংস্কৃতিকে প্রধানত দুটি দিক থেকে দেখা যায়:
* বাহ্যিক সভ্যতা বা সংস্কৃতি (Pārthiva/Bhautika Sabhyatā): এটি হলো কোনো জাতির জীবনের সেই অংশ, যা বাহ্যিক চোখে দৃশ্যমান এবং যা বস্তুগত বা পার্থিব। এর মধ্যে পড়ে— ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, সুসংবদ্ধ জীবন-রীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বস্তু ও ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা, এবং নানা হস্তশিল্প। এই বাহ্যিক রূপটি অনেক জাতির মধ্যেই সমপর্যায়ের হতে পারে।
* আভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি (Ābhyantara Samskrti): এটি হলো সেই অতিরিক্ত বস্তু, যা জাতির জীবনের বাহ্য সভ্যতার ভিতরে প্রতিভাত হয়। এটিই বাহ্য সভ্যতার আভ্যন্তর প্রাণ বা অনুপ্রেরণা। এই অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতিকে ইংরেজি ভাষায় ‘Culture’ (কালচার) বলা হয়। এর মধ্যে প্রধানত অন্তর্ভুক্ত: দর্শন ও ধর্ম, সাহিত্য, পরমত সহিষ্ণুতা, তত্ত্বানুসন্ধিৎসা, অহিংসা, আত্ম-দমন (দম), ত্যাগ এবং সত্য শিব ও সুন্দরের আহ্বান। সংক্ষেপে, এটি হলো একটি জাতির চিন্তা, বোধ-শক্তি এবং জীবনবোধের সূক্ষ্ম প্রকাশ।
সুতরাং, প্রভেদ হলো— বাহ্যিকটি হলো বস্তুগত প্রকাশ, আর আভ্যন্তরীণটি হলো সেই বস্তুগত প্রকাশের প্রেরণা ও জীবনবোধের মূল ভিত্তি।
(খ) ভারত-সভ্যতা-তরুর সংস্কৃতি পুষ্প কীভাবে ফুটে উঠিছে?
* উত্তর:
লেখক ভারতীয় সভ্যতাকে একটি ‘তরু’ বা গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যার ‘সংস্কৃতি’ হলো সেই গাছের ‘পুষ্প’ বা ফুল। এই সংস্কৃতি পুষ্প ফুটে ওঠার মূল কারণ হলো ভারতীয় জাতির সমন্বয়ী চরিত্র।
* মূল ভিত্তি (সমন্বয়): ভারতীয় জাতি নানা জাতির সম্মিলন ও সংমিশ্রণের ফলে গড়ে উঠেছে। এই বিভিন্ন জাতির ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি প্রথমে পৃথক হলেও, তারা একে অপরের মধ্যে বিলীন হয়ে এক বিরাট সমন্বয়ে সার্থকতা লাভ করেছে। এই সমন্বয়ই হলো হিন্দু সভ্যতার প্রথম ও প্রধান সাংস্কৃতিক সূত্র।
* পরমত সহিষ্ণুতা: এই সমন্বয়ের ফলস্বরূপ ভারতীয় জাতির মজ্জায় প্রবেশ করেছে পরমত সহিষ্ণুতার বোধ— অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মমতকে একই সত্যে পৌঁছানোর ভিন্ন পথ হিসেবে দেখা।
* ঐক্য আবিষ্কার: ভারতীয়রা চিরকাল ধরে আপাত-বিরোধী মতবাদের মধ্যকার ঐক্য বা সামঞ্জস্য খুঁজে বের করে একটি মিলন-সংগীতের চেষ্টা করে এসেছে।
এইভাবেই বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য এবং পরমত সহিষ্ণুতার মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা-তরুর সংস্কৃতি পুষ্প বিকশিত হয়েছে।
খ- ভাষা-অধ্যয়ন (ব্যবহারিক ব্যাকরণ)
৬। সংস্কৃতি (সম্ + কৃতি), এভাবে শব্দের আগে সম্ উপসর্গ যোগ করে সংস্কার, সংযম, সঞ্চয় ইত্যাদি শব্দ লিখতে পারা যায়। সেইভাবে নিম্নলিখিত উপসর্গের সাহায্যে পাঁচটি করে শব্দ লেখো এবং সেই শব্দগুলো দিয়ে তোমার খাতায় বাক্য রচনা করো।
উপসর্গ ও শব্দসহ বাক্য রচনা
প্রতি —
১. প্রতিবাদ — অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করা উচিত।
২. প্রতিক্ষণ — সে প্রতিক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করে।
৩. প্রতিফল — তার চেষ্টার প্রতিফল সে পেয়েছে।
৪. প্রতিনিধি — ক্লাসের প্রতিনিধি হিসেবে সে কথা বলল।
৫. প্রতিজ্ঞা — সে কঠোর পরিশ্রমের প্রতিজ্ঞা করল।
অব —
১. অবরোধ — পাহাড়ি রাস্তায় বরফের অবরোধ সৃষ্টি হয়েছে।
২. অবলোকন — তিনি গভীর মনোযোগে প্রকৃতি অবলোকন করছেন।
৩. অবস্থা — দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়।
৪. অবকাশ — পুজোর সময় আমাদের অবকাশ থাকে।
৫. অবসান — দিনের অবসান হলে পাখিরা ঘরে ফেরে।
অনু —
১. অনুসরণ — আমাদের মহাপুরুষদের আদর্শ অনুসরণ করা উচিত।
২. অনুগামী — সে গুরুর অনুগামী হয়ে জীবন কাটাচ্ছে।
৩. অনুভব — তাঁর দুঃখ আমি গভীরভাবে অনুভব করি।
৪. অনুজ্ঞা — গুরু শিষ্যকে কাজের অনুজ্ঞা দিলেন।
৫. অনুকূল — আজ আবহাওয়া আমাদের অনুকূল ছিল।
বি —
১. বিখ্যাত — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বিখ্যাত কবি।
২. বিশেষ — আজ আমার একটি বিশেষ কাজ আছে।
৩. বিজ্ঞান — সে বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করছে।
৪. বিদেশ — সে কর্মসূত্রে বিদেশ যাত্রা করেছে।
৫. বিফল — শত চেষ্টা করেও তার কাজটি বিফল হলো।
উৎ —
১. উৎপন্ন — এই জমিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়।
২. উৎসব — আমরা মহা সমারোহে দুর্গা উৎসব পালন করি।
৩. উদ্যোগ — কাজটি সফল করতে তার উদ্যোগ প্রশংসনীয়।
৪. উৎকৃষ্ট — তিনি সবসময় উৎকৃষ্ট মানের জিনিস ব্যবহার করেন।
৫. উৎপাত — ক্লাসে দুষ্টুমি করে উৎপাত করা উচিত নয়।
৭। নীচের বাক্যগুলোর নিম্নরেখ পদের কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো।
| কারক ও বিভক্তি বিশ্লেষণ
(ক) বৃষ্টি পড়ছে — বৃষ্টি — কর্তৃকারক (কর্তৃবাচ্যে কর্তা) — শূন্য
(খ) কমল চাবি দিয়ে তালা খুলছে — চাবি দিয়ে — করণ কারক (যার দ্বারা কাজ সম্পন্ন হয়) — ‘দিয়ে’ (অনুসর্গ)
(গ) গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র রচনাবলি আছে — গ্রন্থাগারে — অধিকরণ কারক (স্থান) — ‘এ’
(ঘ) টাকায় কিনা হয় — টাকায় — করণ কারক (উপকরণ/যার দ্বারা) — ‘য়’ (এ)
(ঙ) পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায় — পাগলে — কর্তৃকারক (কর্তা) — ‘এ’
— ছাগলে — কর্তৃকারক (কর্তা) — ‘এ’
৮। পাঠ থেকে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে নিয়ে সন্ধি-বিচ্ছেদ করো।
|সন্ধি-বিচ্ছেদ ও সন্ধি
সংস্কৃতি — সম্ + কৃতি — ব্যঞ্জন সন্ধি
সমীরণের — সম্ + ঈরণ — ব্যঞ্জন সন্ধি
সর্বাঙ্গীন — সর্ব + অঙ্গীন — স্বর সন্ধি
নবসৃষ্ট — নব + সৃষ্ট — স্বর সন্ধি
আবির্ভাব — আবিঃ + ভাব — বিসর্গ সন্ধি
উল্লিখিত — উৎ + লিখিত — ব্যঞ্জন সন্ধি
৯। বাচ্য সংক্রান্ত জ্ঞানমূলক অংশ (শিক্ষকদের জন্য):
(শিক্ষার্থীদের জ্ঞাতব্য বিষয়: বাচ্য হলো বাক্যে ক্রিয়ার কর্তা-কর্ম প্রভৃতির কোনো একটি প্রধানরূপে বোঝাবার শক্তিকে বলে। এর প্রধান ভাগগুলি হলো: কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ও ভাববাচ্য।)
১০। উদাহরণ দেখে নীচের বাক্যগুলোর বাচ্য পরিবর্তন করো।
বাচ্য পরিবর্তন (কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য)
কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে —
(খ) শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন — শিক্ষক মহাশয় কর্তৃক ছেলেদের বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো।
(গ) পুলিস চোর ধরে — পুলিস কর্তৃক চোর ধৃত হয়।
কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে —
(খ) আমার হাতে তুমি ধরা পড়বেই — আমি তোমাকে ধরবই।
(গ) তাঁর দ্বারা টিকিট কেনা হয়নি — তিনি টিকিট কেনেননি।
কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে —
(খ) ছবিটা আমি দেখেছি — আমার দ্বারা ছবিটা দেখা হয়েছে।
(গ) তুমি কি আজ গান গেয়েছ — তোমার দ্বারা কি আজ গান গাওয়া হয়েছে।
ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে —
(খ) ছেলেটির কি করা হয় — ছেলেটি কি করে।
(গ) খাবার সময় বোঝা যাবে — খাবার সময় তুমি বুঝবে (বা, লোকে বুঝবে)।
১১. নির্দেশ অনুযায়ী বাচ্য পরিবর্তন করো —
(ক) আমি আজ যাইব না (ভাববাচ্য) — আমার আজ যাওয়া হবে না।
(খ) আমি কাজটি করেছি (কর্মবাচ্য) — আমার দ্বারা কাজটি করা হয়েছে।
(গ) আমার যাওয়া চাই (কর্তৃবাচ্য) — আমি যেতে চাই (বা, আমার যেতে হবে)।
(ঘ) কোথায় থাকা হয় (কর্তৃবাচ্য) — তুমি কোথায় থাকো।
(ঙ) তুমি কোথা হতে এলে (ভাববাচ্য) — তোমা কর্তৃক কোথা হতে আসা হলো।
(চ) ছেলেদের ন্যায় মেয়েদেরও লেখাপড়া শেখানো উচিত (কর্তৃবাচ্য) — ছেলেদের ন্যায় মেয়েদেরও লেখাপড়া শেখা উচিত।
গ- জ্ঞান-সম্প্রসারণ
১২। ‘একটি অঞ্চলের পরিধেয়, খাদ্যাভ্যাস, জলবায়ু, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, গান-বাজনা, খেলা-ধুলা, বিবাহ ইত্যাদিতে সেই অঞ্চলের মানুষের রুচিবোধ প্রতিফলিত করে।’ এবার আমাদের সাজ-পোশাক, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি কীভাবে একটি নির্দিষ্ট স্থানের সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরে, উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে লেখো।
Ans.একটি অঞ্চলের সংস্কৃতি হলো সেই অঞ্চলের মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রার দর্পণ। সাজ-পোশাক ও খাদ্যাভ্যাস হলো এই সংস্কৃতির সবচেয়ে দৃশ্যমান পরিচয়।
সাজ-পোশাকের মাধ্যমে পরিচয়:
পোশাক সাধারণত সেই অঞ্চলের জলবায়ু ও ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে তৈরি হয়।
* জলবায়ু: উষ্ণ জলবায়ুর অঞ্চলে সুতির পাতলা পোশাক এবং শীতল জলবায়ুর অঞ্চলে পশমের বা গরম পোশাক প্রচলিত। উদাহরণস্বরূপ, আসামের মহিলারা শীতল আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে ঐতিহ্যবাহী মেখেলা চাদর পরিধান করেন, যা মূলত মূর্তির কাপড়। অন্যদিকে, উত্তর ভারতের পাঞ্জাবি পুরুষেরা ঢিলেঢালা কুর্তা-পায়জামা পরেন, যা গরমের জন্য আরামদায়ক।
* ঐতিহ্য: পোশাকের রং, নকশা ও পরিধানের রীতি সেখানকার রুচি ও ধর্মীয় অনুভূতিকে প্রকাশ করে। যেমন— বাঙালি মহিলারা শাড়িকে বিশেষ ভঙ্গিতে পরিধান করেন এবং দুর্গা পূজার সময় নতুন পোশাকের কদর বাড়ে।
খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে পরিচয়:
খাদ্যাভ্যাস একটি অঞ্চলের কৃষিজ উৎপাদন এবং ভূগোল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
* কৃষিজ উৎপাদন: যে অঞ্চলে যা বেশি উৎপন্ন হয়, সেটাই সেখানকার প্রধান খাদ্য হয়ে ওঠে। যেমন— বাঙালি ও অসমীয়া সংস্কৃতিতে ভাত ও মাছ প্রধান খাদ্য, কারণ এই অঞ্চলগুলি নদীমাতৃক এবং ধান উৎপাদনে সমৃদ্ধ। আবার, উত্তর-পশ্চিম ভারতে গম (রুটি) প্রধান, কারণ সেখানে গম চাষ বেশি হয়।
* রীতিনীতি: খাদ্যের প্রস্তুতি ও পরিবেশন সেখানকার সামাজিক রীতিনীতির পরিচয় দেয়। যেমন— দক্ষিণ ভারতের উৎসবে কলাপাতায় খাবার পরিবেশন করা হয়, যা তাদের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সরলতার প্রকাশ।
সুতরাং, পোশাক ও খাদ্যাভ্যাস শুধুমাত্র মানুষের প্রয়োজন মেটায় না, বরং এটি একটি নির্দিষ্ট স্থানের রুচিবোধ, ভৌগোলিক পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরে।
১৩। গান-বাজনা-নাচ, চিত্রকলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য এবং উৎসব-পার্বণ ইত্যাদি আমাদের সমাজ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ। এই উপাদানগুলো সংস্কৃতি গড়ে তুলতে কীভাবে সাহায্য করে? তুমি ভেবে বুঝিয়ে লেখো।
Ans.গান-বাজনা-নাচ, চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং উৎসব-পার্বণ— এই উপাদানগুলি সংস্কৃতির ‘বাহ্যিক প্রকাশ’ এবং ‘আভ্যন্তরীণ প্রেরণা’র মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। এগুলি মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস এবং সমষ্টিগত জীবনবোধকে মূর্ত করে তোলে।
* ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সংরক্ষণ: গান (যেমন— লোকসংগীত, ভক্তিমূলক গান) এবং উৎসব-পার্বণ (যেমন— বিহু, দুর্গাপূজা) প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটি সমাজের বিশ্বাস, ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধকে বহন করে। এগুলি অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে।
* সামাজিক বন্ধন ও সমন্বয়: উৎসবগুলি মানুষকে একত্রিত করে, ভেদাভেদ ভুলিয়ে সমষ্টিগত আনন্দ সৃষ্টি করে, যা সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ থেকে যে সমন্বয় এসেছে, তা উৎসবের মাধ্যমে উদ্যাপিত হয়।
* আত্ম-প্রকাশ ও রুচিবোধ: নাচ ও চিত্রকলা হলো মানুষের আত্ম-প্রকাশের মাধ্যম, যা তাদের রুচিবোধ এবং নান্দনিক চেতনাকে প্রতিফলিত করে। শিল্পীর সৃষ্টি সেই সমাজের আবেগ, জীবনযাত্রা ও চিন্তাভাবনাকে ফুটিয়ে তোলে।
* ইতিহাসের দলিল: স্থাপত্য ও ভাস্কর্য (যেমন— পুরোনো মন্দির, মসজিদ বা স্মৃতিস্তম্ভ) একটি জাতির জ্ঞান, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এবং ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলিকে চিরন্তন করে রাখে। এগুলি সেই সময়ের জীবনধারা এবং আদর্শের স্থায়ী দলিল হিসেবে কাজ করে।
মোটকথা, এই উপাদানগুলি একটি সমাজের প্রাণ। এগুলি মানুষকে বর্বর প্রকৃতি থেকে দিব্য প্রকৃতিতে উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করে, যা জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার সংজ্ঞায়িত সংস্কৃতির মূলকথা।
১৪। নীচের পংক্তিগুলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারততীর্থ’ কবিতা থেকে উদ্ধৃত। পংক্তিগুলো পড়ে শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীর কাছ থেকে তাৎপর্য জেনে নিয়ে লেখো।
(পংক্তিগুলি: কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা / দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা। / হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন- / শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন। / পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার, / দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে- / এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।)
Ans.তাৎপর্য:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারততীর্থ’ কবিতা থেকে উদ্ধৃত এই পংক্তিগুলিতে ভারতের সমন্বয়ী সংস্কৃতি এবং বিশ্বমানবতার মহামিলন ক্ষেত্র রূপে তার বিশেষত্বকে তুলে ধরা হয়েছে।
ইতিহাসের স্রোতধারা: কবি বলছেন, যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানবগোষ্ঠী (আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, হুন, পাঠান, মোগল) কোথা থেকে এক দুর্বার স্রোতের মতো ভারতে প্রবেশ করেছে, তা কেউ জানে না। এই প্রতিটি ধারা ভারতে এসে এক বিশাল সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছে— অর্থাৎ, তাদের নিজ নিজ পৃথক সত্তা হারিয়ে তারা এক অভিন্ন ভারতীয় জাতিতে লীন হয়েছে।
* মিলন ও সমন্বয়ের ভূমি: ভারত হলো সেই মহামানবের সাগরতীর যেখানে বৈচিত্র্য বিলীন হলেও ধ্বংস হয় না, বরং সমন্বয় লাভ করে। এখানে সবাই মিলেছে এবং মিশেছে, কেউ ফিরে যায়নি।
* আদান-প্রদান: পশ্চিমে দ্বার খোলার কথা বলে কবি ইঙ্গিত করেছেন যে, আধুনিক যুগে ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলেও ভারত কেবল গ্রহণই করছে না, বরং উপহার দিচ্ছে ও নিচ্ছে। এই ‘দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে’ নীতিই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি, যা পরমত সহিষ্ণুতা এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসার মাধ্যমে এক অদ্বিতীয় মিলনক্ষেত্র তৈরি করেছে।
পংক্তিগুলির সারমর্ম হলো— ভারত কোনো একক জাতির দেশ নয়, বরং এটি পৃথিবীর সমস্ত মানবগোষ্ঠীর মিলনস্থল, যেখানে বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য ও বিশ্বমানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
ঘ- প্রকল্প
১৫। অসমিয়া ও বাঙালি সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করে লেখো এবং শ্রেণিতে পাঠ করে শোনাও।
উত্তর: (শিক্ষার্থীদের নিজে এই তুলনামূলক আলোচনা প্রস্তুত করতে হবে। নীচে একটি তুলনামূলক আলোচনার রূপরেখা দেওয়া হলো।)
অসমিয়া ও বাঙালি সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা
অসমিয়া ও বাঙালি সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা
তুলনার বিষয় — অসমিয়া সংস্কৃতি — বাঙালি সংস্কৃতি
মূল ভিত্তি — মূলত ইন্দো-আর্য ও অস্ট্রো-এশীয় গোষ্ঠীর সমন্বয়। বোড়ো, গারো, কছারি, রাভা, মিসিং, কার্বি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে অসমিয়া সংস্কৃতির সমন্বয় হয়েছে। — মূলত ইন্দো-আর্য ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির সমন্বয়। বঙ্গভূমির প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও ধর্মাবলম্বী জনসাধারণকে নিয়েই বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।
ভাষা — অসমীয়া (Assamese) ভাষা। — বাংলা (Bengali) ভাষা।
উৎসব — বিহু (ভোগালী, রঙ্গালী, কঙ্গালী) প্রধান উৎসব। এটি প্রকৃতির পরিবর্তন ও কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত। আলি আই লৃগাং (মিসিং জনজাতির) অন্য একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। — দুর্গাপূজা (প্রধান উৎসব), কালীপূজা, রথযাত্রা, বসন্ত উৎসব। এটি ধর্মীয় ও সামাজিক মিলনকে কেন্দ্র করে।
পোশাক — মেখেলা চাদর (মহিলাদের), গামছা (পুরুষদের)। রীহা, মুগা ও পাটের কাপড় ঐতিহ্যবাহী। — শাড়ি (মহিলাদের), ধুতি-পাঞ্জাবি (পুরুষদের)।
খাদ্যাভ্যাস — ভাত, মাছ, বিভিন্ন ধরনের শাক-পাতা (শাাক), পিঠা, খাড় (ক্ষার জাতীয় পদ) এবং বাঁশের কোঁড়ল ব্যবহৃত হয়। — ভাত, মাছ (বিশেষত ইলিশ), বিভিন্ন ধরনের ডাল, শাক-সবজি, মিষ্টি (রসগোল্লা, সন্দেশ)।
নৃত্য-কলা — বিহু নৃত্য (প্রধান ও গতিশীল), সত্ৰীয়া নৃত্য (শাস্ত্রীয় নৃত্য)। — কথক, কীর্তন, ছৌ নৃত্য (লোকনৃত্য), রবীন্দ্রনৃত্য।
উপসংহার — উভয় সংস্কৃতিই সমন্বয়মূলক প্রকৃতির এবং উভয়েই নদীমাতৃক অঞ্চলের প্রভাব বহন করে। তবে, অসমিয়া সংস্কৃতিতে জনগোষ্ঠীগত বৈচিত্র্য ও প্রকৃতি-নির্ভরতা বেশি, অন্যদিকে বাঙালি সংস্কৃতিতে ধর্মীয় উৎসবের প্রভাব ও সাহিত্য-শিল্পের ঐতিহ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।