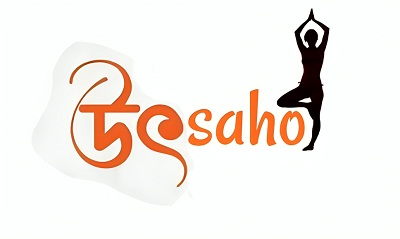মধ্য যুগের অসমীয়া সমাজ এর ভিতরের এবং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর
এখানে পাঠ্যপুস্তকের মধ্য যুগের অসমীয়া সমাজ এর প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সমাধান করা হলো।
ক্রিয়াকলাপ
পৃষ্ঠা ৩১
• বর্তমান অসমের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি শনাক্ত করো। এই রাজ্যগুলোর সঙ্গে আমাদের রাজ্যের সম্পর্ক কেমন? দলগতভাবে আলোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করো।
উত্তর: এটি একটি প্রকল্পভিত্তিক কাজ।
ভূমিকা: বর্তমান অসমের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলো হলো অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ও ভুটান এবং বাংলাদেশের সঙ্গেও অসমের সীমান্ত রয়েছে। এই রাজ্যগুলোর সঙ্গে অসমের সম্পর্ক ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গভীর।
(প্রতিবেদনের জন্য কিছু তথ্য):
* সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান: সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর সঙ্গে অসমের ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, উৎসব এবং লোকসংস্কৃতির অনেক মিল দেখা যায়।
* অর্থনৈতিক সম্পর্ক: ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াত এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই রাজ্যগুলো পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।
* **ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:**历史上, এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, যেমনটি পাঠ্যে আহোমদের ‘পচা প্রথা’-র বিবরণে পাওয়া যায়।
পৃষ্ঠা ৩২
• আমাদের সমাজে বর্তমান সময়ে পুরুষ-মহিলাদের পরিধেয় সাজ-পোশাকের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
উত্তর: এটি একটি তালিকা তৈরির কাজ। নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:
* মহিলাদের পোশাক: মেখেলা-চাদর, শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, কুর্তি, জিন্স, টপস ইত্যাদি।
* পুরুষদের পোশাক: ধুতি-পাঞ্জাবি, শার্ট-প্যান্ট, টি-শার্ট, কুর্তা-পাজামা, জিন্স ইত্যাদি।
পৃষ্ঠা ৩৩
• মধ্যযুগের জলসিঞ্চন ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান জলসিঞ্চন ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করো।
উত্তর:
মধ্যযুগের জলসিঞ্চন ব্যবস্থা:
মধ্যযুগে কৃষকরা মাটিতে বাঁধ দিয়ে বৃষ্টির জল জমিয়ে রাখত এবং সেই জল খেতের জমিতে সরবরাহ করত। কোচবিহারে ঝরনার উৎসে বাঁধ নির্মাণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী খেতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থা ছিল মূলত প্রকৃতি-নির্ভর এবং সরল।
বর্তমান জলসিঞ্চন ব্যবস্থা:
বর্তমানে জলসিঞ্চন ব্যবস্থা অনেক উন্নত ও প্রযুক্তি-নির্ভর। নদী বা জলাধার থেকে ক্যানেল বা খালের মাধ্যমে দূর-দূরান্তের জমিতে জল পৌঁছে দেওয়া হয়। ডিপ-টিউবওয়েল, পাম্পসেট, স্প্রিংকলার এবং ড্রিপ ইরিগেশনের মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জলের অপচয় রোধ করা হয় এবং эффективноভাবে জমিতে জল সরবরাহ করা হয়।
তুলনা: মধ্যযুগের ব্যবস্থা ছিল স্থানীয় ও ছোট আকারের, যেখানে বর্তমান ব্যবস্থা বৃহৎ আকারের এবং প্রযুক্তিনির্ভর। তবে উভয় ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই হলো কৃষিকাজের জন্য জলের জোগান নিশ্চিত করা।
• অসমের জোনবিল মেলায় কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রব্য-সামগ্রী কেনা-বেচা হয়? শিক্ষক অথবা অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে জোনবিল মেলার ওপর একটি প্রকল্প প্রস্তুত করো।
উত্তর: অসমের জোনবিল মেলায় বিনিময় প্রথা বা Barter System-এর মাধ্যমে দ্রব্য-সামগ্রী কেনা-বেচা হয়। মধ্যযুগের শুরুতে এই প্রথার প্রচলন ছিল।
(প্রকল্পের জন্য নির্দেশিকা):
* বিষয়: জোনবিল মেলার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব।
* উদ্দেশ্য: বিনিময় প্রথার কার্যকারিতা বোঝা এবং পাহাড়ি ও সমতলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের অন্বেষণ করা।
* তথ্য সংগ্রহ: মেলায় অংশগ্রহণকারী মানুষের সাক্ষাৎকার, ছবি সংগ্রহ এবং পুরোনো তথ্য অনুসন্ধান।
* প্রতিবেদন: মেলার ইতিহাস, বিনিময় প্রথার পদ্ধতি এবং এর সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করা।
পৃষ্ঠা ৩৫
• তোমাদের জেলায়-স্থিত পুরোনো কীর্তিচিহ্নগুলোর নাম এবং ছবিসহ একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করো।
উত্তর: এটি একটি ক্ষেত্র-ভিত্তিক প্রকল্প। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের জেলায় অবস্থিত ঐতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন করে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করবে। উদাহরণস্বরূপ, শিবসাগর জেলার ছাত্রছাত্রীরা শিবদৌল, রংঘর, কারেংঘর, জয়সাগর পুকুর ইত্যাদি কীর্তিচিহ্ন নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে।
অনুশীলনী
১। সংক্ষেপে উত্তর লেখো-
(ক) মধ্যযুগে অসমে শাসনকারী উল্লেখযোগ্য রাজ্যগুলোর নাম।
উত্তর: মধ্যযুগে অসমে শাসনকারী উল্লেখযোগ্য রাজ্যগুলো হলো কামরূপ-কামতা, চুতিয়া, বারোভূঞা, কছাড়ি এবং আহোম।
(খ) কোন জনজাতীয় মহিলারা দখনা পরিধান করেন?
উত্তর: বোড়ো (কছাড়ি) জনজাতীয় মহিলারা দখনা পরিধান করেন।
(গ) আহোমদের রাজত্বকালে ভূ-সম্পত্তির অধিকারী কে ছিলেন?
উত্তর: আহোমদের রাজত্বকালে রাজা ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন।
(ঘ) মধ্যযুগের প্রারম্ভিক পর্যায়ে কোন প্রথার দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য চলত?
উত্তর: মধ্যযুগের প্রারম্ভিক পর্যায়ে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।
(ঙ) কপিলির পারে আলিপুখুরির বরদোয়ায় কে টোল স্থাপন করে জ্ঞান চর্চা করেছিলেন?
উত্তর: মহেন্দ্র কন্দলী কপিলির পারে আলিপুখুরির বরদোয়ায় টোল স্থাপন করে জ্ঞান চর্চা করেছিলেন।
২। ‘ক’ অংশের সঙ্গে ‘খ’ অংশ মেলাও:
উত্তর:
| ‘ক’ অংশ | ‘খ’ অংশ |
| :— | :— |
| মাধব কন্দলী | রামায়ণ |
| সুকুমার বরকাইথ | হস্তীবিদ্যার্ণব |
| পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ | রত্নমালা |
| ভট্টদেব | কথা গীতা |
| বলদেব সূর্যহরি দৈবজ্ঞ | দরং রাজবংশাবলি |
৩। শূন্যস্থান পূর্ণ করো –
(ক) হয়গ্রীব মাধব মন্দির কোচরাজা নরনারায়ণ নির্মাণ করেছিলেন।
(খ) মধ্যযুগে মহিলার স্থান ছিল সম্মানজনক ও উচ্চ।
(গ) জনজাতীয় লোকদের মধ্যে জুম কৃষির প্রচলন ছিল।
(ঘ) অনন্ত কন্দলী ভাগবত অসমিয়া ভাষায় অনুবাদ করেন।
(ঙ) আত্মনির্ভরশীলতা মধ্যযুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।
৪। শুদ্ধ উত্তরটিতে ✔ চিহ্ন দাও-
(ক) মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক।
(খ) পাইক প্রথা প্রচলন করেছিল আহোম।
(গ) টঙালি, হাচতি বারোভূঞাদের অবদান ছিল।
(ঘ) কছাড়িরা নালা-নর্দমা নির্মাণ ব্যবস্থায় অগ্রণী ছিল।
(ঙ) স্বর্গদেউ রুদ্রসিংহের সময়ে আহোম স্থাপত্য শিল্পে মোগল এবং পারসি স্থাপত্য শিল্পের প্রভাব পড়ে।
৫। উত্তর লেখো: (৫০ টি শব্দের মধ্যে)
(ক) আহোমদের পাইক প্রথা।
উত্তর: পাইক প্রথা ছিল আহোমদের একটি অভিনব ব্যবস্থা। ১৫ থেকে ৫০ বছর বয়সী সকল সক্ষম পুরুষকে পাইক বলা হত। তিন বা চারজন পাইকের মধ্যে একজন পালা করে রাজবাড়িতে শ্রমদান করত, এবং যুদ্ধের সময় সৈনিক হিসেবে কাজ করত। দেশের শ্রম ও সামরিক শক্তির ভিত্তি ছিল এই পাইকরা।
(খ) আহোমগণ কী কারণে পচা প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন?
উত্তর: আহোমরা সীমান্তবর্তী পাহাড়ি জনজাতিদের আক্রমণ থেকে সমতলের প্রজাদের রক্ষা করার জন্য পচা প্রথা প্রবর্তন করেছিল। এই ব্যবস্থার অধীনে, পাহাড়ি জাতিগুলোকে কিছু গ্রাম ছেড়ে দেওয়া হতো, যেখান থেকে তারা শস্য সংগ্রহ করত এবং বিনিময়ে সমতলের প্রজাদের আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দিত।
(গ) মধ্যযুগে অসমিয়া সমাজে নারীর ভূমিকা কেমন ছিল?
উত্তর: মধ্যযুগে অসমের মহিলাদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হত। তাঁরা শুধুমাত্র ঘরোয়া কাজেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, প্রয়োজনে যুদ্ধেও অংশ নিতেন। এছাড়া তাঁত বোনা এবং গুপ্তচর বৃত্তির মতো কাজেও তাঁদের অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। তুলনামূলকভাবে ভারতীয় সমাজে তাঁদের স্থান ছিল বেশ উচ্চে।
(ঘ) মধ্যযুগের কৃষি ব্যবস্থা।
উত্তর: মধ্যযুগে অসমের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। ধান, ডাল, আখ, পাট, ফল-মূল ইত্যাদি চাষ করা হতো। পাহাড়ি অঞ্চলে সোপান কৃষি এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে জুম চাষের প্রচলন ছিল। কৃষকরা জমিতে বাঁধ দিয়ে বৃষ্টির জল জমিয়ে খেতিতে জলসেচ করত।
(ঙ) কছাড়িদের স্থাপত্য বিদ্যার উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ কী কী?
উত্তর: কছাড়িদের স্থাপত্য শিল্প ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের। আহোমদের আগে থেকেই তারা ইটের ব্যবহার জানত এবং তাদের রাজধানী ডিমাপুর ইটের দেওয়ালে ঘেরা ছিল। তাদের স্থাপত্যে বঙ্গদেশের মুসলিম নির্মাণশৈলীর প্রভাব দেখা যায়। এছাড়া তারা নালা-নর্দমা নির্মাণেও অগ্রণী ছিল।
৬। মধ্যযুগের অসমের অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করো।
উত্তর: মধ্যযুগের অসমের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক ও আত্মনির্ভরশীল।
* কৃষি: জনসাধারণের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। ধান, ডাল, পাট, কার্পাসসহ বিভিন্ন ফল ও শাক-সবজি উৎপাদন করা হত। জুম চাষ এবং বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।
* শিল্প: বস্ত্রশিল্প, বয়নশিল্প, হাতির দাঁতের শিল্প, বাঁশ-বেতের কাজ, মৃৎশিল্প এবং ধাতুশিল্পের মতো কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে অসম সমৃদ্ধ ছিল। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই তাঁতশাল ছিল।
* বাণিজ্য: বাণিজ্যিক আদান-প্রদান সীমিত থাকলেও আহোমরা বঙ্গ, তিব্বত ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করত। কোচ রাজারা মুদ্রা প্রচলন করে এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ করে বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছিলেন।
৭। আহোমদের ভূমি নীতির ওপর মতামত দাও।
উত্তর: আহোমদের ভূমি নীতি ছিল মূলত রাজকেন্দ্রিক। রাজা রাজ্যের সমস্ত জমির অধিকারী ছিলেন। কৃষকদের জমির জন্য রাজাকে কর দিতে হত। তবে এই নীতির একটি ইতিবাচক দিক হলো, প্রতিটি পাইককে রাজ্যের সেবার বিনিময়ে ৪ বিঘা পর্যন্ত করমুক্ত জমি দেওয়া হত। এছাড়াও, ব্রাহ্মণ, দেবালয়, সত্র, মন্দির এবং পরবর্তীকালে মসজিদ ও কবরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও করমুক্ত জমি দান করা হতো, যা ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করত। এই নীতি একদিকে যেমন রাজকোষকে শক্তিশালী করত, তেমনই প্রজাদের প্রতি একটি কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতিফলিত করত।
৮। মধ্যযুগে নির্মিত মঠ-মন্দিরগুলোর ছবি সংগ্রহ করে একটি অ্যালবাম তৈরি করো।
উত্তর: এটি একটি প্রকল্পভিত্তিক কাজ। ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত স্থাপত্যগুলির ছবি সংগ্রহ করে অ্যালবাম তৈরি করতে পারে:
* রংঘর
* কারেংঘর
* তলাতল ঘর
* শিবদৌল, বিষ্ণু দৌল, দেবীদৌল
* হয়গ্রীব-মাধব মন্দির
* কামাখ্যা মন্দির
* ডিমাপুরের ভগ্নাবশেষ
৯। মধ্যযুগে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থসমূহের সঙ্গে তাদের রচয়িতাদের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
উত্তর:
| গ্রন্থ | রচয়িতা |
| :— | :— |
| রামায়ণ (অসমিয়া) | মাধব কন্দলী |
| হস্তীবিদ্যার্ণব | সুকুমার বরকাইথ |
| গীতগোবিন্দ, শঙ্খচূড়বধ | রামনারায়ণ চক্রবর্তী |
| পদ্মপুরাণ | নারায়ণদেব |
| দরং রাজবংশাবলি | বলদেব সূর্যহরি দৈবজ্ঞ |
| মহাভারত (অসমিয়া অনুবাদ) | রাম সরস্বতী |
| রত্নমালা ব্যাকরণ | পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ |
| কথা গীতা | ভট্টদেব |
১০। ‘সাম্প্রতিক অসমের ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, প্রতিটি জাতি-জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত সৃষ্টি এবং সম্পত্তি’ – এই বাক্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: এই বাক্যটির তাৎপর্য হলো, অসমের বর্তমান সমৃদ্ধ ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি কোনো একটি বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর একক অবদান নয়, বরং এটি এখানকার বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর মিলিত প্রচেষ্টার ফল। মধ্যযুগে কামতা ও কোচ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা, আহোমদের বুরঞ্জী সাহিত্য, কছাড়ি রাজার অনুপ্রেরণায় রামায়ণের অনুবাদ, এবং স্থানীয় জনজাতীয় ভাষিক গোষ্ঠীর অবদান—এই সমস্ত কিছুর মিশ্রণেই আজকের অসমিয়া সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের মতো যুগপুরুষ কোচ রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই অসমের সংস্কৃতি হলো এক বহুত্ববাদী সংস্কৃতির উজ্জ্বল উদাহরণ, যা সকলের সম্মিলিত সৃষ্টি এবং সকলেরই গর্বের সম্পত্তি।