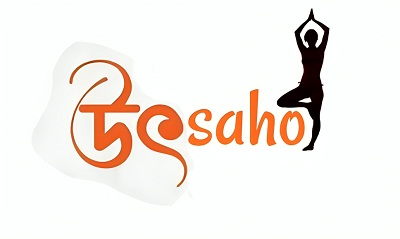ছুটি’, Chapter- 7, Class-9, SEBA
‘ছুটি’, Chapter- 7, Class-9, SEBA
১. শুদ্ধ উত্তরটি খুঁজে বের করো।
(ক) ‘ছুটি’ গল্পের লেখক হলেন-
(১) বনফুল (২) শরৎ চন্দ্র (৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪) সত্যজিৎ রায়।
উত্তর: (৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(খ) বালকদের সর্দার ছিল-
(১) মাখনলাল (২) ফটিক (৩) সুশান্ত (৪) রমেশ
উত্তর: (২) ফটিক
(গ) মাখনলাল ফটিক চক্রবর্তীর কে ছিল?
(১) কাকা (২) বড়ভাই (৩) মেজভাই (৪) ছোটভাই
উত্তর: (৪) ছোটভাই
(ঘ) ফটিকের মা, ফটিককে কোথায় চড় মেরেছিল?
(১) পিঠে (২) কপালে (৩) গালে (৪) গণ্ডদেশে
উত্তর: (১) পিঠে (গল্পে উল্লেখ আছে: “তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন।”)
(ঙ) ফটিকের মামার নাম ছিল-
(১) রায়বাবু (২) কমলবাবু (৩) বিশ্বম্ভরবাবু (৪) আবীরবাবু।
উত্তর: (৩) বিশ্বম্ভরবাবু
২. শূন্যস্থান পূর্ণ করো।
(১) নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড ____ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল।
উত্তর: নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল।
(২) বিশেষতঃ ____ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই।
উত্তর: বিশেষতঃ তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই।
(৩) মামির স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দূরগ্রহের মতো ____ হইতেছে।
উত্তর: মামির স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দূরগ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে।
(৪) স্কুলে এত বড়ো নির্বোধ এবং ____ বালক আর ছিল না।
উত্তর: স্কুলে এত বড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না।
৩. শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বাক্য খুঁজে বের করো।
(১) কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।
উত্তর: শুদ্ধ।
(২) “একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত সাহসী হইয়া গিয়া কহিল, “বই হারিয়ে ফেলেছি।”
উত্তর: অশুদ্ধ। (সঠিক বাক্য: “একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল…”)
(৩) “এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল”।
উত্তর: শুদ্ধ।
(৪) ডাক্তারবাবু আনন্দমনে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।
উত্তর: অশুদ্ধ। (সঠিক বাক্য: “ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন…”)
৪. ভাববিষয়ক অনুশীলন
(ক) অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন।
(১) ‘ছুটি’ গল্পের লেখক কে?
উত্তর: ‘ছুটি’ গল্পের লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(২) ‘ছুটি গল্পের প্রধান চরিত্রটির নাম উল্লেখ করো।
উত্তর: ‘ছুটি’ গল্পের প্রধান চরিত্রটির নাম ফটিক চক্রবর্তী।
(৩) ‘ছুটি’ গল্পটি লেখকের কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
উত্তর: ‘ছুটি’ গল্পটি লেখকের ‘গল্পগুচ্ছ’ প্রথম খণ্ড থেকে সংকলন করা হয়েছে।
(৪) ফটিকের মামার নাম কী ছিল?
উত্তর: ফটিকের মামার নাম ছিল বিশ্বম্ভরবাবু।
(৫) বালকদের সর্দার কে ছিল?
উত্তর: বালকদের সর্দার ছিল ফটিক চক্রবর্তী।
(৬) ফটিকের মামা ফটিককে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন?
উত্তর: ফটিকের মামা ফটিককে কলিকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন।
(৭) ফটিকের বয়স কত ছিল?
উত্তর: ফটিকের বয়স ছিল তেরো-চৌদ্দ বৎসর।
(৮) ফটিকের মামা ফটিককে কখন ওর মায়ের কাছে নিয়ে যাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন?
উত্তর: ফটিকের মামা কথা দিয়েছিলেন যে, স্কুলের ছুটি (অর্থাৎ কার্তিক মাসে পূজার ছুটি) হলে তিনি ফটিককে ওর মায়ের কাছে নিয়ে যাবেন।
(৯) মাখনলাল এবং ফটিকের মধ্যে কী সম্পর্ক ছিল?
উত্তর: মাখনলাল ছিল ফটিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (ছোট ভাই)।
(১০) ফটিক মাখনলালকে চড় মেরেছিল কেন?
উত্তর: মা যখন ফটিককে জিজ্ঞাসা করেন সে মাখনকে মেরেছে কিনা, তখন মাখন তার পূর্ব নালিশ সমর্থন করে বলে, “হাঁ, মেরেছে।” এই মিথ্যা কথা শুনে ফটিকের আর সহ্য হয়নি, তাই সে মাখনকে এক সশব্দ চড় কষিয়ে দেয়।
(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন।
(১) “মামা, মার কাছে কবে যাব?” উক্তিটি কার? কখন, কাকে এই উক্তি করা হয়েছে?
উত্তর: উক্তিটি ‘ছুটি’ গল্পের প্রধান চরিত্র ফটিকের।
কলকাতায় মামার বাড়িতে এসে মামির স্নেহহীন অনাদরে এবং স্কুলের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে না পেরে ফটিক যখন তার গ্রামের বাড়ির জন্য, বিশেষত তার মায়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, তখন সে একদিন অনেক সাহস সঞ্চয় করে তার মামা বিশ্বম্ভরবাবুকে এই উক্তিটি করেছিল।
(২) ফটিকের মামা কোথায় কী করতেন?
উত্তর: ফটিকের মামা বিশ্বম্ভরবাবু পশ্চিমে কাজ করিতেন।
(৩) ফটিকের প্রতি ওর মামির ব্যবহার কীরূপ ছিল?
উত্তর: ফটিকের প্রতি ওর মামির ব্যবহার অত্যন্ত স্নেহহীন, অনাদপূর্ণ এবং কঠোর ছিল। মামি ফটিককে ‘অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধি’ এবং ‘একটা দুরগ্রহের মতো’ মনে করতেন। ফটিক কোনো কাজ উৎসাহের সাথে করতে গেলেও তিনি তাকে দমন করতেন। ফটিকের বই হারিয়ে যাওয়ার কথা শুনেও তিনি সহানুভূতি না দেখিয়ে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন যে, তিনি মাসে পাঁচবার বই কিনে দিতে পারবেন না।
(৪) মা, ফটিককে কেন ওর মামার সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন, তা সংক্ষেপে লেখো।
উত্তর: ফটিকের মা ফটিকের অবাধ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং পাঠে অমনোযোগের কারণে তার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন এবং তাকে ‘হাড় জ্বালাতন’ মনে করতেন। তার মনে সর্বদা এই আশঙ্কা ছিল যে, ফটিক কোনোদিন তার ছোট ভাই মাখনকে জলেই ফেলে দেবে বা তার মাথাই ফাটিয়ে দেবে। এই পরিস্থিতিতে, যখন তার দাদা বিশ্বম্ভরবাবু ফটিককে নিজের কাছে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন, তখন তিনি সহজেই সম্মত হয়েছিলেন।
(৫) ফটিক মাখনলালকে সশব্দে চড় মেরেছিল কেন-বুঝিয়ে লেখো।
উত্তর: মাখন বাড়িতে নালিশ করেছিল যে ফটিক তাকে মেরেছে। মা ফটিককে প্রশ্ন করলে সে তা অস্বীকার করে। কিন্তু মা যখন মাখনকে জিজ্ঞাসা করেন, সে তার আগের নালিশ সমর্থন করে বলে, “হাঁ, মেরেছে।” ভাইয়ের এই মিথ্যাচারে ফটিকের আর সহ্য হয়নি, তাই সে ক্রোধে “ফের মিথ্যা কথা” বলে দ্রুত গিয়ে মাখনকে এক সশব্দ চড় কষিয়ে দেয়।
(৬) নদীতীরে বালকদের খেলা বন্ধ হয়ে গেল কেন?
উত্তর: ফটিকের প্রস্তাবে বালকেরা মাখনসুদ্ধ প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠটি ঠেলতে শুরু করে। কিন্তু গুঁড়ি এক পাক ঘুরতে না ঘুরতেই মাখন কাঠ থেকে পড়ে যায়। এরপর মাখন তৎক্ষণাৎ উঠে ফটিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে অন্ধভাবে মারতে থাকে এবং তার নাকে-মুখে আঁচড় কেটে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে চলে যায়। এর ফলেই বালকদের খেলা ভেঙে যায়।
(৭) ফটিকের মামা এতদিন কোথায় ছিলেন?
উত্তর: ফটিকের মামা বিশ্বম্ভরবাবু এতদিন পশ্চিমে কাজ করিতেছিলেন।
(৮) কোন অবস্থায় ফটিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থতার কারণ লেখো।
উত্তর: স্কুলে বই হারিয়ে ফেলার জন্য ফটিককে প্রতিদিন মাস্টারের হাতে মারধোর ও অপমান সহ্য করতে হচ্ছিল। মামির কাছে বইয়ের কথা বললে তিনিও তিরস্কার করেন। এই অপমান ও অনাদর সহ্য করতে না পেরে সেই রাতেই ফটিকের মাথাব্যথা ও জ্বর আসে। পরদিন সে নিরুদ্দেশ হয় এবং সমস্ত দিন মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টিতে ভিজে ও সর্বাঙ্গে কাদা মেখে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। এই شدید শারীরিক ও মানসিক কষ্টের ফলেই ফটিক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে।
(৯) ফটিকের মাকে কেন বিশ্বম্ভরবাবু কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন? মা এসে কী করলেন?
উত্তর: ফটিকের জ্বর অত্যন্ত বেড়ে গিয়ে সে প্রলাপ বকতে শুরু করে। ডাক্তার যখন ফটিকের অবস্থাকে ‘বড়োই খারাপ’ বলে জানান এবং বিশ্বম্ভরবাবু বুঝতে পারেন যে ফটিক মৃত্যুর মুখে তার মা-কে খুঁজছে, তখন তিনি ফটিকের মাকে আনতে পাঠান।
মা এসে ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই উচ্চস্বরে শোক করতে শুরু করেন। বিশ্বম্ভরবাবু বহু কষ্টে তাকে শান্ত করলে, তিনি শয্যার উপর আছাড় খেয়ে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে ফটিককে “সোনা”, “মানিক” বলে ডাকতে থাকেন।
(১০) “ফটিক তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।” উক্তিটি কার? কখন কেন এই উক্তির অবতারণা?
উত্তর: উক্তিটি ফটিকের মামা বিশ্বম্ভরবাবুর।
গুরুতর অসুস্থ ফটিক জ্বরের ঘোরে কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হয়ে ফ্যালফ্যাল করে ঘরের চারিদিকে সম্ভবত তার মা-কে খুঁজছিল। কিন্তু কাউকে না পেয়ে নিরাশ হয়ে সে আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ে। তখন বিশ্বম্ভরবাবু তার মনের ভাব বুঝতে পেরে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবং তার মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশ্বাস দিতেই কানের কাছে মুখ নত করে মৃদুস্বরে এই উক্তিটি করেন।
(গ) রচনাধর্মী উত্তর লেখো।
(১) ‘মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।’ উদ্ধৃত উক্তির যথার্থ বর্ণনা দাও।
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছুটি’ গল্পের অন্তিম পর্বে, মৃত্যুপথযাত্রী ফটিকের এই উক্তিটি গল্পের মূল আবেদনকে ধারণ করে আছে। এই ‘ছুটি’ এবং ‘বাড়ি যাওয়া’ কেবল আক্ষরিক অর্থে মামার বাড়ি থেকে গ্রামের বাড়িতে যাওয়া নয়, এর এক গভীরতর এবং করুণ তাৎপর্য রয়েছে।
কলকাতায় আসার পর থেকেই ফটিকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। মামির স্নেহহীন অনাদর এবং স্কুলের প্রতিকূল পরিবেশে সে হাঁফিয়ে উঠেছিল। তার তেরো-চৌদ্দ বছরের সংবেদনশীল কিশোর মন কেবলই তার গ্রামের বাড়ির মুক্তি এবং তার ‘অত্যাচারিণী অবিচারিণী’ মায়ের জন্য আকুল হয়ে কাঁদত। সে মামার কাছে বাড়ি যাওয়ার ছুটি চেয়েছিল, কিন্তু মামা ‘স্কুলের ছুটি’ (পূজার ছুটি) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন।
সেই ছুটি আসার আগেই ফটিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। যখন তার মা অবশেষে এলেন, ফটিক তখন মৃত্যুশয্যায়। মায়ের ডাকে সে মৃদুস্বরে এই কথাগুলি উচ্চারণ করে। এই ‘ছুটি’ হলো পৃথিবীর সমস্ত অনাদর, অপমান, যন্ত্রণা এবং বন্ধন থেকে তার চিরমুক্তি বা চিরছুটি—অর্থাৎ মৃত্যু। আর ‘বাড়ি যাওয়া’ হলো সেই কাঙ্ক্ষিত আশ্রয়, যা সে এই পৃথিবীতে পায়নি, মৃত্যুর মাধ্যমে সে সেই পরম আশ্রয়ে ফিরে যাচ্ছে।
(২) ফটিকের মামির চরিত্র বর্ণনা করো।
উত্তর: ‘ছুটি’ গল্পে ফটিকের মামি এক গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্র, যিনি ফটিকের悲剧-এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। তার চরিত্রের প্রধান দিকগুলি হলো:
১. স্নেহহীনা ও আত্মকেন্দ্রিক: তিনি নিজের তিনটি ছেলে ও ঘরকন্না নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। ফটিকের আগমনকে তিনি ‘অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধি’ বলে মনে করেছিলেন এবং এতে যে ‘বিপ্লবের সম্ভাবনা’ দেখা দেবে, তা নিয়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন।
২. অসংবেদনশীল ও কঠোর: তিনি তেরো-চৌদ্দ বছরের কিশোর মনস্তত্ত্ব বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ফটিকের প্রতি তার আচরণ ছিল অত্যন্ত রূঢ়। ফটিক যখন উৎসাহের সাথে কোনো কাজ করতে যেত, তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে পড়তে বলতেন, যা ফটিকের কাছে নিষ্ঠুর অবিচার বলে মনে হতো।
৩. বিদ্বেষপূর্ণ: ফটিকের সামান্য ত্রুটিতেও তিনি অসহিষ্ণু হয়ে পড়তেন। ফটিক যখন তার বই হারিয়ে ফেলে অপরাধীর মতো তা জানায়, তখন তিনি সহানুভূতি দেখানোর বদলে তিরস্কার করে বলেন, “আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।”
৪. নির্মমতা: তার চরিত্রের চরম নির্মমতা প্রকাশ পায় যখন বৃষ্টিতে ভেজা, অসুস্থ, কাঁপতে থাকা ফটিককে পুলিস ফিরিয়ে নিয়ে আসে। সেই অবস্থায় ফটিককে দেখেও তার দয়া হয়নি, বরং তিনি বিরক্ত হয়ে স্বামীকে বলেছিলেন, “কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ? দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।”
সুতরাং, ফটিকের মামি ছিলেন এক অসংবেদনশীল, স্নেহহীনা নারী, যার অনাদর ও অবিচার ফটিককে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল।
(৩) নদীতীরে বালকদের খেলার দৃশ্যটি বিস্তারিত বর্ণনা করো।
উত্তর: গল্পের শুরুতে নদীতীরে ফটিক ও তার দলের বালকদের এক দুরন্ত খেলার দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। ফটিক ছিল সেই বালকদের সর্দার। তার মাথায় এক নতুন বুদ্ধি আসে। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হওয়ার অপেক্ষায় পড়ে ছিল; ফটিক প্রস্তাব দেয় যে, সবাই মিলে সেটা গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কাঠের মালিকের যে অসুবিধা হবে, তা উপলব্ধি করেই বালকেরা এই প্রস্তাবে সানন্দে সায় দেয়।
যখন সবাই মিলে কোমর বেঁধে কাজে নামার উপক্রম করছে, ঠিক সেই সময় ফটিকের ছোট ভাই মাখনলাল এসে গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়িটার উপর বসে পড়ে। ছেলেরা তার এই ঔদাসীন্যে বিরক্ত হলেও কেউ তাকে কিছু বলতে সাহস পায় না। ফটিক প্রথমে আস্ফালন করে মাখনকে মারের ভয় দেখালেও সে আরও জাঁকিয়ে বসে। তখন ফটিক তার রাজসম্মান রক্ষা করতে এক নতুন প্রস্তাব দেয়—মাখনকে শুদ্ধই কাঠ গড়ানো হোক।
মাখন এতে গৌরব বোধ করে, কিন্তু বিপদের কথা ভাবেনি। ছেলেরা “মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো” বলে যেই কাঠ ঠেলতে শুরু করেছে, গুঁড়ি এক পাক ঘুরতে না ঘুরতেই মাখন তার গাম্ভীর্য ও তত্ত্বজ্ঞানসমেত মাটিতে পড়ে যায়। এরপরই মাখন উঠে ফটিককে মারতে শুরু করে এবং কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে যাওয়ায় খেলা ভেঙে যায়।
(৪) বিশ্বম্ভরবাবু কে? ‘ছুটি’ গল্পে তাঁর ভূমিকা আলোচনা করো।
উত্তর: বিশ্বম্ভরবাবু হলেন ফটিকের মামা এবং তার বিধবা ভগিনীর দাদা। তিনি পশ্চিমে কাজ করতেন এবং বহুকাল পরে দেশে ফিরে বোনের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। ‘ছুটি’ গল্পে বিশ্বম্ভরবাবুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং করুণ।
তিনিই ফটিকের মা-র কাছে ছেলেদের পড়াশোনার খোঁজখবর নেন এবং ফটিকের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা শুনে তাকে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রেখে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবের মাধ্যমেই ফটিকের জীবনের করুণ পর্ব শুরু হয়। তার উদ্দেশ্য মহৎ হলেও, তিনি তার বাড়ির পরিবেশ—বিশেষত তার স্ত্রীর চরিত্র—এবং একটি পাড়াগাঁয়ের ছেলের মানসিকতা বিবেচনা করেননি।
কলিকাতায় মামাই ছিলেন ফটিকের একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু তিনি ফটিকের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেননি। তিনি ফটিকের মামির অনাদর বা স্কুলের যন্ত্রণা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। তবে গল্পের শেষে তিনিই ফটিকের যন্ত্রণা অনুভব করেন। ফটিক যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তিনিই চিকিৎসক নিয়ে আসেন, সস্নেহে তার পাশে বসেন এবং ফটিকের মনের কথা বুঝতে পেরে তার মা-কে আনতে পাঠান।
বিশ্বম্ভরবাবু স্বভাবগতভাবে সজ্জন ও স্নেহশীল হলেও, তার অপরিণামদর্শিতা এবং ব্যস্ততা ফটিকের জীবনে এক গভীর বিপর্যয় ডেকে আনে।
(৫) বালক ফটিকের চরিত্র বর্ণনা করো।
উত্তর: ‘উত্তর: ‘ছুটি’ গল্পের প্রধান চরিত্র ফটিক চক্রবর্তী তেরো-চৌদ্দ বছরের এক কিশোর, যার চরিত্রটি গ্রাম ও শহরের ভিন্ন পরিবেশে দুটি রূপে ফুটে উঠেছে।
গ্রামীণ জীবনে ফটিক ছিল মুক্ত, স্বাধীনচেতা এবং বালকদের সর্দার। তার চরিত্রে দুরন্তপনা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল প্রবল। সে নতুন নতুন উপদ্রবের ফন্দি আঁটত, যেমন—শালকাষ্ঠ গড়ানো, এবং পড়াশোনায় তার একেবারেই মন ছিল না। মাঠে ঘুড়ি উড়ানো ও দলবল নিয়ে ঘুরে বেড়ানোই ছিল তার প্রিয় কাজ। মায়ের প্রতি তার এক অবুঝ ভালোবাসা ছিল; ফটিকের হৃদয় মায়ের প্রতিই আকৃষ্ট ছিল।
কলিকাতায় মামার বাড়িতে আসার পর ফটিকের চরিত্রের সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক প্রকাশ পায়। সে হয়ে ওঠে লজ্জিত, শঙ্কিত ও অপমানিত। মামির স্নেহহীন অনাদরে তার কোমল মন ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। মামিকে খুশি করার জন্য অতিরিক্ত কাজ করতে গিয়েও সে তিরস্কৃত হয়। নতুন পরিবেশে স্কুলে তাকে ‘নির্বোধ ও অমনোযোগী’ বালক বলে গণ্য করা হয়। তার সংবেদনশীল মন কেবলই গ্রামের হারানো স্বাধীনতা ও মায়ের স্নেহের জন্য কাঁদত।
ফটিকের চরিত্রটি মূলত পরিবেশের শিকার। যে দুরন্ত ছেলেটি গ্রামে ছিল সর্দার, সেই ছেলেই শহরের স্নেহহীন পরিবেশে অনাদর ও অপমানে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।
(৬) গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে না ঘুরিতেই মাখনলালের অবস্থা কী হইল? পরে সে কী করিল-তার বর্ণনা দাও।
উত্তর: বালকেরা যখন মাখনসুদ্ধ শালকাষ্ঠটি “মারো ঠেলা হেঁইয়ো” রবে ঠেলতে শুরু করল, তখন গুঁড়ি এক পাক ঘুরতে না ঘুরতেই মাখন তার সমস্ত গাম্ভীর্য, গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞানসমেত মাটিতে পড়ে গেল (ভূমিসাৎ হইল)।
পরে, মাখন তৎক্ষণাৎ মাটি থেকে উঠেই ফটিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে অন্ধভাবে মারতে শুরু করল। সে ফটিকের নাকে-মুখে আঁচড় কেটে কাঁদতে কাঁদতে গৃহাভিমুখে গমন করল।
(ঘ) ব্যাখ্যা লেখো।
(১) “সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।”
উত্তর: উৎস: উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছুটি’ গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গ: লেখক তেরো-চৌদ্দ বছরের কিশোরদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এই উক্তিটি করেছেন।
ব্যাখ্যা: লেখকের মতে, এই বয়সটি বড়ই অদ্ভুত। এই বয়সের ছেলেরা শৈשবের লালিত্য এবং যৌবনের সৌন্দর্য—কোনোটিই পায় না। তারা পৃথিবীর কোথাও ঠিক খাপ খেতে পারে না এবং নিজেদের অস্তিত্ব নিয়েই লজ্জিত থাকে। তারা স্নেহের জন্য অত্যন্ত কাঙাল হয়, কিন্তু কেউ তাদের স্নেহ করতে সাহস পায় না, কারণ লোকে সেটাকে ‘প্রশ্রয়’ বলে মনে করে। এইভাবে চারিদিক থেকে অনাদৃত, স্নেহবঞ্চিত এবং লজ্জিত থাকার ফলে তাদের চেহারা ও ভাবভঙ্গি অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হয়ে যায়—যারা শঙ্কিত, অপ্রয়োজনীয় এবং সকলের দ্বারা বিতাড়িত।
(২) “বিশেষতঃ তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না”
উত্তর: উৎস: উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছুটি’ গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গ: ফটিকের মামি তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলেদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন, তা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক এই উক্তি করেছেন।
ব্যাখ্যা: ফটিকের মামির দৃষ্টিতে, তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলেরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ‘বালাই’ বা আপদ। কারণ এই বয়সে তাদের শৈশবের সৌন্দর্য বা মিষ্টতা থাকে না, আবার তারা বড়দের মতো কোনো প্রয়োজনীয় কাজেও লাগে না। তাদের মুখের আধো আধো কথা যেমন ন্যাকামি, তেমনি পাকা কথাও জ্যাঠামি বলে মনে হয়। কাপড়-চোপড়ের অসামঞ্জস্যে তাদের দেখতে বেমানান লাগে। এই অনাকর্ষণীয় გარეგন এবং কোনো উপযোগিতা না থাকার ফলেই তারা বড়দের স্নেহ আকর্ষণ করতে পারে না। ফটিকের মামির এই ভাবনা তৎকালীন প্রাপ্তবয়স্ক সমাজের কিশোরদের প্রতি উদাসীনতারই প্রতিফলন।
(৩) “বেশ করেছ, আমি তোমাকে তো মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।”
উত্তর: উৎস: উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছুটি’ গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গ: ফটিক যখন স্কুলে তার পাঠ্যবই হারিয়ে ফেলে এবং সেই কথা তার মামিকে এসে জানায়, তখন মামি অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তি প্রকাশ করে এই উক্তিটি করেন।
ব্যাখ্যা: এই উক্তিটির মাধ্যমে ফটিকের মামির চরিত্রের নির্মমতা, কৃপণতা এবং অসংবেদনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। ফটিক বই হারিয়ে অত্যন্ত বিপদে পড়েছিল এবং মাস্টারের হাতে প্রতিদিন অপমানিত হচ্ছিল। সে হয়তো মামির কাছে সামান্য সহানুভূতি বা সাহায্যের প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু মামি তার সমস্যাটিকে মানবিক দৃষ্টিতে না দেখে কেবল আর্থিক ক্ষতি হিসেবে দেখলেন। তার কাছে ফটিকের যন্ত্রণা বা শিক্ষার গুরুত্বের চেয়ে বইয়ের দামটাই বড় হয়ে উঠল। এই রূঢ় মন্তব্য ফটিককে বুঝিয়ে দিল যে সে পরের পয়সা নষ্ট করছে, যা তার অভিমানকে তীব্রতর করে তোলে এবং তাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়।
(৪) “মা, আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।”
উত্তর: উৎস: উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছুটি’ গল্পের প্রধান চরিত্র ফটিকের জীবনের অন্তিম সংলাপ।
প্রসঙ্গ: দীর্ঘ অসুস্থতার পর, যখন ফটিকের মা তার শয্যাপার্শ্বে এসে তাকে “সোনা”, “মানিক” বলে ডাকেন, তখন ফটিক প্রায় অচেতন অবস্থায় মৃদুস্বরে এই কথাগুলি উচ্চারণ করে।
ব্যাখ্যা: এই উক্তিটির দুটি গভীর অর্থ রয়েছে। প্রথমত, ফটিকের আক্ষরিক ‘ছুটি’র আকাঙ্ক্ষা। সে মামার কাছে বাড়ি যাওয়ার জন্য ছুটি চেয়েছিল, মামা পূজার ছুটির কথা দিয়েছিলেন। ফটিকের কাছে তার মায়ের আগমনই সেই কাঙ্ক্ষিত ছুটির বার্তা বয়ে এনেছে। দ্বিতীয় এবং গভীরতর অর্থে, এই ‘ছুটি’ হলো জীবন থেকে মুক্তি। কলিকাতার ‘নরক’ যন্ত্রণা, অনাদর, অপমান এবং বন্ধন থেকে সে চিরতরে মুক্তি বা ‘ছুটি’ লাভ করছে। তার ‘বাড়ি যাওয়া’ হলো এই যন্ত্রণাময় পৃথিবী ছেড়ে মৃত্যুর মাধ্যমে সেই পরম আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া, যার জন্য সে ব্যাকুল ছিল।
(৫) মা, আমাকে মারিস নে মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করিনি।”
উত্তর: উৎস: উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছুটি’ গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গ: কলিকাতায় মামার বাড়িতে বৃষ্টিতে ভিজে ফটিক যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে থাকে, তখন সে এই কথাগুলি উচ্চারণ করে।
ব্যাখ্যা: ফটিকের এই প্রলাপোক্তি তার গভীর অবচেতন মনের ভয় ও যন্ত্রণার প্রকাশ। সে তার মা-কে গভীরভাবে ভালোবাসলেও তার মা ছিলেন ‘অত্যাচারিণী অবিচারিণী’। সম্ভবত মাখনের সাথে ঝগড়ার ঘটনায় বা অন্যান্য কারণে সে তার মায়ের কাছে অন্যায্যভাবে শাস্তি পেত। জ্বরের ঘোরে ফটিকের সেইসব পুরনো স্মৃতি ফিরে এসেছে। সে যেন নিজেকে তার মায়ের সামনে দেখতে পাচ্ছে এবং মারের ভয়ে আঁতকে উঠে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য করুণভাবে আকুতি জানাচ্ছে।
(ঙ) প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করো।
(১) “অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস্।”
উত্তর: প্রসঙ্গ: ফটিকের মা এই উক্তিটি করেছিলেন। মাখন মিথ্যা নালিশ করায় ফটিক তাকে চড় মারে। এতে মা মাখনের পক্ষ নিয়ে ফটিকের পিঠে কয়েকটি চড় মারলে ফটিক মাকে ঠেলে দেয়। ঠিক সেই মুহূর্তে মা চিৎকার করে এই কথা বলেন, এবং তখনই তার দাদা বিশ্বম্ভরবাবু ঘরে ঢোকেন।
(২) “মামির স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দূর গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে।”
উত্তর: প্রসঙ্গ: কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছানোর পর ফটিক যখন তার মামির মুখোমুখি হয়, তখন মামির আচরণ ও মনোভাব দেখে ফটিকের এই অনুভূতি হয়। মামি এই ‘অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধি’তে মোটেই সন্তুষ্ট হননি, এবং ফটিক বুঝতে পারছিল যে সে মামির কাছে এক অবাঞ্ছিত আগন্তুক বা ‘দুরগ্রহের’ মতো।
(৩) “মামা, মার কাছে কবে যাবো?”
উত্তর: প্রসঙ্গ: কলিকাতায় এসে মামির অনাদর, স্কুলের বিড়ম্বনা এবং গ্রামের বাড়ির জন্য তীব্র আকুলতায় ফটিক যখন অত্যন্ত পীড়িত, তখন সে একদিন অনেক সাহস সঞ্চয় করে তার মামা বিশ্বম্ভরবাবুকে এই প্রশ্নটি করেছিল।
(৪) “মামা আমার ছুটি হয়েছে কী?”
উত্তর: প্রসঙ্গ: বাড়ি পালানোর চেষ্টার পর বৃষ্টিতে ভিজে ফটিক যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে থাকে, তখন সে তার মামা বিশ্বম্ভরবাবুকে উদ্দেশ্য করে রক্তবর্ণ চোখে এই প্রশ্নটি করে। তার মন তখন কেবলই বাড়ি যাওয়ার ‘ছুটি’র জন্য অপেক্ষা করছিল।
(৫) “আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।”
উত্তর: প্রসঙ্গ: ফটিক নিরুদ্দেশ হওয়ার পর পুলিসের লোক যখন তাকে বৃষ্টিভেজা, কর্দমাক্ত অবস্থায় ধরে এনে মামার কাছে উপস্থিত করে, তখন মামি তাকে দেখে বিরক্ত হন। সেই সময় ফটিক কেঁদে উঠে এই কথাগুলি বলে।
(৬) “ফটিক তোর, মাকে আনতে পাঠিয়েছি।”
উত্তর: প্রসঙ্গ: ফটিক যখন মৃত্যুশয্যায় এবং জ্বরের ঘোরে কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হয়ে ফ্যালফ্যাল করে ঘরের চারিদিকে (সম্ভবত মা-কে) খুঁজে নিরাশ হয়ে মুখ ফিরিয়ে শোয়, তখন তার মামা বিশ্বম্ভরবাবু তার মনের ভাব বুঝতে পেরে তার কানের কাছে মুখ নত করে মৃদুস্বরে এই কথাগুলি বলে তাকে আশ্বস্ত করেন।
চ. ভাষা বিষয়ক (ব্যাকরণ)
১) পদান্তর করো
* কাতরতা (বিশেষ্য) – কাতর (বিশেষণ)
* তাপ (বিশেষ্য) – তপ্ত (বিশেষণ)
* দীন (বিশেষণ) – দৈন্য (বিশেষ্য)
* অস্থির (বিশেষণ) – অস্থিরতা (বিশেষ্য)
* ব্যাকুল (বিশেষণ) – ব্যাকুলতা (বিশেষ্য)
* লজ্জা (বিশেষ্য) – লজ্জিত (বিশেষণ)
* চক্ষু (বিশেষ্য) – চাক্ষুষ (বিশেষণ)
* অন্তর (বিশেষ্য) – আন্তরিক (বিশেষণ)
* প্রবল (বিশেষণ) – প্রাবল্য (বিশেষ্য)
* মন (বিশেষ্য) – মানসিক (বিশেষণ)
* শৈশব (বিশেষ্য) – শিশু (বিশেষ্য / বিশেষণ)
* সাহস (বিশেষ্য) – সাহসী (বিশেষণ)
২) বাক্য রচনা করো
* ফ্যাল ফ্যাল: মা-কে দেখতে না পেয়ে অসুস্থ ফটিক ফ্যাল ফ্যাল করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল।
* থর্ থর্: বৃষ্টিতে ভিজে ফটিক জ্বরের ঘোরে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল।
* ঝু ঝু : সেদিন রাত্রি হইতে মুষলধারে ঝু ঝু করিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল।
* বোঁ বোঁ: ফটিক গ্রামের মাঠে বোঁ বোঁ শব্দে প্রকাণ্ড ধাউস ঘুড়ি উড়াইয়া বেড়াইত।
* মনে মনে: মামি যে তাহার আগমনে সন্তুষ্ট হন নাই, তাহা ফটিক মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিল।
* ব্যথাব্যথা: ছেলের কথাগুলো শুনে মায়ের মনে কেমন যেন ব্যথাব্যথা বোধ হলো।
৩) বিপরীত শব্দ লেখো
* মিথ্যা – সত্য
* সাধ্য – অসাধ্য
* সশব্দ – নিঃশব্দ
* সহ্য – অসহ্য
* সন্তুষ্ট – অসন্তুষ্ট
* নিবৃত্ত – প্রবৃত্ত
* আরম্ভ – শেষ
* অনাদর – আদর / স্নেহ
* নিরাশা – আশা
* উচ্চ – মৃদু / নিম্ন
৪) সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার সন্ধির সংজ্ঞা সহ পাঁচটি করে উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।
উত্তর:
সন্ধি: পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, দ্রুত উচ্চারণের ফলে দুটি পদের সন্নিহিত ধ্বনি যখন একে অপরের সাথে মিলিত হয়, বা একটি লোপ পায় বা উভয়ই পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধ্বনির সৃষ্টি করে, তখন তাকে সন্ধি বলে। যেমন: বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।
সন্ধির প্রকারভেদ: বাংলা ব্যাকরণে সন্ধিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়:
১. স্বরসন্ধি
২. ব্যঞ্জনসন্ধি
৩. বিসর্গসন্ধি
১. স্বরসন্ধি:
সংজ্ঞা: স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে স্বরসন্ধি বলে।
উদাহরণ:
* অ + অ = আ (নর + অধম = নরাধম)
* আ + আ = আ (বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়)
* ই + ই = ঈ (রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র)
* ঈ + ই = ঈ (মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র)