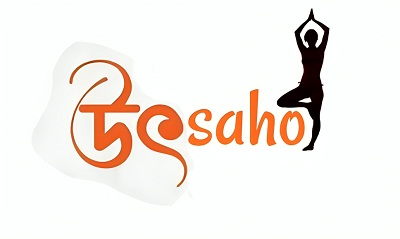আদরিনী, Class -10, SEBA board exam
খ। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (Brief Answers)
ক। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।
১. নগেন বাবুর পেশা কী?
উত্তর: নগেন বাবুর পেশা ডাক্তার।
২. জয়রামের পেশা কী?
উত্তর: জয়রামের পেশা মোক্তার।
৩. কুঞ্জবিহারীবাবু পেশায় ছিলেন। (শূন্যস্থান পূর্ণ করো।)
উত্তর: কুঞ্জবিহারীবাবু পেশায় ছিলেন জুনিয়ার উকিল।
৪. মেঝবাবু কে?
উত্তর: মেঝবাবু হলেন পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ির একজন। তাঁর মেয়ের বিয়েতে নগেন ডাক্তার, কুঞ্জবিহারীবাবু ও জয়রাম মোক্তার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন।
৫. জয়রামের বয়স কত?
উত্তর: জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বয়স এখন পঞ্চাশৎ পার হইয়াছে (পঞ্চাশ বছরের বেশি)। গল্পের পরবর্তী অংশে তাঁর বয়স প্রায় ষাট বৎসর উল্লেখ করা হয়েছে।
৬. জয়রাম কার কাছে হাতি চেয়ে পাঠালেন?
উত্তর: জয়রাম মহারাজ শ্রীনরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী বাহাদুর-এর কাছে হাতি চেয়ে পাঠালেন।
৭. জয়রামের আদি নিবাস কোথায় ছিল?
উত্তর: জয়রামের আদিবাস যশোর জেলায়।
৮. জয়রামের গাভীটির কী নাম ছিল?
উত্তর: জয়রামের গাভীটির নাম ছিল মঙ্গলা।
৯. কার নামে জয়রাম তাঁর গরুর বাছুরের নাম রেখেছিলেন?
উত্তর: জয়রাম তাঁর গরুর বাছুরের নাম রেখেছিলেন ডেপুটিবাবুর নামে।
১০. উমাচরণ লাহিড়ীর বাসস্থান কোথায়?
উত্তর: উমাচরণ লাহিড়ীর বাসস্থান বীরপুরে।
১১. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা কোথায় হয়?
উত্তর: চৈত্রসংক্রান্তিতে বামুনহাটে একটি বড় মেলা হয়।
১২. আদরিণী কে?
উত্তর: আদরিণী হলো জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের কেনা মাদী-হাতীটি।
১৩. হাতি তোর পায়ে’। (শূন্যস্থান পূর্ণ করো।)
উত্তর: ‘হাতি তোর গোদা পায়ে নাতি’।
১৪. ‘হাতি তোর গোদা পায়ে নাতি’- এখানে ‘নাতি’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: এখানে ‘নাতি’ শব্দের অর্থ লাথি।
১৫. জয়রামের কয় ছেলে?
উত্তর: জয়রামের তিনটি পুত্র।
১৬. ‘আদরিণী’ গল্পে উল্লিখিত মেলা দু’টির নাম লেখো।
উত্তর: ‘আদরিণী’ গল্পে উল্লিখিত মেলা দু’টির নাম হলো: বামুনহাট এবং রসুলগঞ্জ।
খ। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।
১. জয়রাম মুখোপাধ্যায় কে? তাঁর স্বভাবের পরিচয় দাও।
জয়রাম মুখোপাধ্যায় পীরগঞ্জ এস্টেটের বাঁধা মোক্তার ছিলেন। তিনি অতি অভিমানী ও স্পর্শকাতর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সামান্য কারণেই তীব্র রাগ বা অভিমান প্রকাশ করতেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল স্নেহময় ও উদার। তিনি দরিদ্রের পাশে দাঁড়াতেন, বিনা ফিসে মামলা চালাতেন এবং অকাতরে অন্নদান করতেন। যৌবনে রূক্ষ ও বদরাগী হলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সহৃদয় ও দয়ালু হয়ে উঠেছিলেন।
২. জয়রাম হাতি চেয়ে পাঠালেন কেন?
পীরগঞ্জের মেঝবাবুর মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য জয়রাম হাতি চেয়ে পাঠান। ঘোড়ার গাড়ির পথ ছিল না এবং গরুর গাড়িতে যেতে সময় বেশি লাগত, তাই আরামদায়কভাবে যাত্রা করার জন্যই তিনি মহারাজ নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরীর কাছে হাতি চেয়েছিলেন।
৩. জয়রামের প্রথমদিকের জীবনযাপন কেমন ছিল?
জয়রামের আদিবাস ছিল যশোরে। তিনি যখন মোক্তারি শুরু করেন, তখন তাঁর সহায়-সম্পত্তি কিছুই ছিল না। পদ্মা পার হয়ে নৌকা, গরুর গাড়ি ও পদব্রজে এসে মাসিক তেরো সিকেয় একটি বাসা ভাড়া নেন। নিজ হাতে রান্না করে খেতেন এবং নিজের পরিশ্রমে মোক্তারি ব্যবসা গড়ে তোলেন।
৪. কার নামে এবং কেন জয়রাম তাঁর বাছুরের নাম রেখেছেন?
জয়রাম তাঁর গরুর বাছুরের নাম রাখেন এক ডেপুটিবাবুর নামে, যার সঙ্গে এজলাসে তাঁর তীব্র তর্ক হয়েছিল। হাকিমের অবিচারে রাগ করে তিনি প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাছুরটির নাম সেই ডেপুটির নামে রাখেন। এটি তাঁর রাগী ও আত্মসম্মানপ্রবণ স্বভাবের প্রকাশ।
৫. কী কারণে আদালতে জয়রাম মোক্তারের জরিমানা হয়েছিল?
একবার আদালতে এক ডেপুটির সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে জয়রাম রাগের মাথায় বলে ফেলেন, “আমার স্ত্রীর যতটুকু আইনজ্ঞান আছে, হুজুরের তাও নাই।” এই মন্তব্য আদালতের অবমাননা হিসেবে গণ্য হওয়ায় তাঁর পাঁচ টাকা জরিমানা হয়।
৬. পত্রবাহক ভৃত্য হাতি সম্পর্কে কী খবর এনেছিল?
ভৃত্য মহারাজের কাছে জয়রামের চিঠি পৌঁছে দেন। ফিরে এসে তিনি জানান, মহারাজ নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেছেন, বিয়ের নিমন্ত্রণের জন্য হাতি দেওয়া সম্ভব নয়; গরুর গাড়িতে আসতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ জয়রাম হাতি পাননি।
৭. ‘তাই ত! সব মাটি?’—কে কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন?
উক্তিটি করেছেন নগেন ডাক্তার। রাজবাড়ি থেকে হাতি পাওয়া যায়নি—এই সংবাদ শুনে তিনি নিরাশ হয়ে বলেন, “তাই ত! সব মাটি?” কারণ হাতি না পেলে তাঁদের পক্ষে বিয়েতে যাওয়া সম্ভব ছিল না।
৮. ‘পরের জিনিষ, জোর ত নেই।’—উক্তিটি কার? কোন প্রসঙ্গে তিনি এই উক্তি করেছেন?
এই উক্তিটি জয়রামের উপস্থিতিতে এক ভদ্রলোক করেছিলেন। মহারাজ হাতি দিতে অস্বীকার করায় ক্ষুব্ধ জয়রামকে শান্ত করার জন্য তিনি বলেন, “পরের জিনিষ, জোর ত নেই।” অর্থাৎ অন্যের জিনিস জোর করে পাওয়া যায় না, ধৈর্য ধরতে হবে।
৯. জয়রাম কোথা থেকে হাতি ক্রয় করলেন এবং কেন?
জয়রাম বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে দুই হাজার টাকায় একটি মাদী-হাতি ক্রয় করেন। মহারাজ হাতি দিতে অস্বীকার করায় তিনি অপমানিত বোধ করেন এবং অভিমান রক্ষার জন্য নিজেই হাতি কিনে নেন, যাতে হাতি চড়ে বিয়েতে যেতে পারেন।
১০. জয়রামের বর্তমান নিবাস কোথায়?
জয়রামের বর্তমান নিবাস ছিল চৌধুরীপাড়া। বিজ্ঞাপনে এই ঠিকানাই উল্লেখ ছিল। তাঁর আদি নিবাস যশোর জেলায় হলেও কর্মসূত্রে তিনি চৌধুরীপাড়াতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।
১১. ‘আপনি জ্ঞানী লোক, মায়া পরিত্যাগ করুন।’—উক্তিটি কার? কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করা হয়েছে?
এই উক্তিটি জয়রামের বন্ধুমহলের একজনের। যখন সংসারে অর্থাভাব দেখা দেয় এবং নাতনীর বিয়ের খরচ মেটানো কঠিন হয়, তখন বন্ধুরা তাঁকে পরামর্শ দেন হাতি বিক্রি করে দেওয়া উচিত। সেই সময়ই তাঁরা বলেন, “আপনি জ্ঞানী লোক, মায়া পরিত্যাগ করুন।”
১২. আদরিণী কে? আদরিণীকে নিয়ে জয়রাম কীরূপ সমস্যায় পড়েছিলেন?
আদরিণী হলো জয়রামের দুই হাজার টাকায় কেনা মাদী-হাতী। মোক্তারি ব্যবসা কমে যাওয়ায় তাঁর আয় হ্রাস পায়, অথচ ব্যয় বেড়ে যায়। নাতনীর বিয়ের খরচ জোগাতে আদরিণী বিক্রি করার কথা ওঠে, কিন্তু জয়রাম তার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহের কারণে মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকেন।
১৩. কল্যাণী কে? কত তারিখে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল?
কল্যাণী হলো জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা পৌত্রী। তাঁর বিবাহ ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নির্ধারিত হয়েছিল। জয়রাম তাঁর বিয়ের খরচ জোগানোর জন্যই আদরিণীকে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।
১৪. ‘দাদামশায় আদর যাবার সময় কাঁদছিল।’—উক্তিটি কার? ‘আদর’ কে? সে কোথায় যাচ্ছিল? আদর যাবার সময় কাঁদছিল কেন?
এই উক্তিটি কল্যাণীর। ‘আদর’ অর্থাৎ আদরিণী, জয়রামের প্রিয় হাতিটি রসুলগঞ্জের মেলায় বিক্রির জন্য যাচ্ছিল। সে কাঁদছিল কারণ তার মালিক জয়রামকে সে খুব ভালোবাসত এবং যেন বুঝে গিয়েছিল যে আর ফিরে আসবে না।
১৫. ‘যেনো হারাধন ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে’—উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
উক্তিটি আদরিণী মেলায় বিক্রি না হয়ে ফিরে আসার পর বলা হয়েছে। জয়রাম ও তাঁর পরিবার আদরিণীকে কেবল পোষা পশু নয়, পরিবারের সদস্য মনে করত। বিক্রি না হয়ে ফিরে আসায় সবার আনন্দ হয়েছিল। তাই বলা হয়, যেন হারানো প্রিয়জন ফিরে এসেছে।
১৬. ‘ওঁর মুখ দিয়ে ব্রহ্মবাক্য বেরিয়েছে…’—ব্রহ্মবাক্য বলতে কী বোঝায়? কার মুখ দিয়ে এই বাক্য নির্গত হয়েছে? এবং বাক্যটি কী?
ব্রহ্মবাক্য অর্থ এমন বাক্য যা সত্য, অটল ও অলঙ্ঘনীয়। এটি জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের মুখ থেকে নির্গত হয়েছিল। তাঁর উক্তি ছিল—“আদর, যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এস।” কথাটি সত্য প্রমাণিত হয়, কারণ আদরিণী সত্যিই সেই মেলায় বিক্রি না হয়ে ফিরে এসেছিল।
১৭. ‘ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল।’—এখানে ব্রাহ্মণ কে? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
এখানে ব্রাহ্মণ হলেন জয়রাম মুখোপাধ্যায়। যখন তিনি খবর পান যে তাঁর প্রিয় হাতি আদরিণী রসুলগঞ্জ যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে পড়ে মারা গেছে, তখন তিনি গভীর শোক ও মানসিক আঘাতে স্তব্ধ হয়ে পড়েন। তাই বলা হয়েছে, তাঁর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছে।
গ। দীর্ঘ উত্তর লেখো (Essay Type Questions and Answers)
১. জয়রামের চরিত্র বর্ণনা করো।
জয়রাম মুখোপাধ্যায় এমন এক চরিত্র, যার মধ্যে একদিকে কঠোরতা ও আত্মমর্যাদাবোধ, অন্যদিকে কোমল স্নেহবোধ ও উদারতা মিলেমিশে গেছে। তিনি ছিলেন পীরগঞ্জ এস্টেটের বাঁধা মোক্তার, অর্থাৎ রাজবাড়ির আইনজীবী বা প্রতিনিধি। তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অভিমান, যা প্রায়ই তাঁর জীবনের সিদ্ধান্তগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত। মহারাজ নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁকে হাতি না দেওয়ায় তিনি অপমানিত অনুভব করে নিজের অভিমান রক্ষার্থে দুই হাজার টাকায় হাতি কিনে ফেলেন। এই ঘটনাই তাঁর অহংকার ও আত্মসম্মানের পরিচায়ক। তবে তাঁর হৃদয়ের গভীরে ছিল অকৃত্রিম স্নেহ ও উদারতা। গরীবের মোকদ্দমা তিনি অনেক সময় বিনা ফিসে চালাতেন এবং মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন। যৌবনে তাঁর মেজাজ ছিল রুক্ষ ও বদরাগী; কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাগ mellow হয়ে আসে। তিনি পরিবারের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। নাতনীর বিয়ের দায়, পুত্রদের অক্ষমতা এবং সংসারের ব্যয়ভার সবই তাঁকে ক্লান্ত করে তুলেছিল, তবুও তিনি দায়িত্ব এড়িয়ে যাননি। জীবনের শেষ পর্বে তাঁর শ্রদ্ধার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন এক ইংরেজ জজ তাঁকে উকিল ভেবে প্রশংসা করেন—এই সামান্য স্বীকৃতি তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। সার্বিকভাবে বলা যায়, জয়রাম মুখোপাধ্যায় ছিলেন একাধারে কঠোর আত্মসম্মানী, গভীর স্নেহপ্রবণ, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং মানবিক গুণে পরিপূর্ণ এক জীবন্ত চরিত্র।
—
২. জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের জীবন সম্পর্কে যা জান লেখো।
জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের জীবন সংগ্রাম, আত্মসম্মান ও দায়িত্ববোধে পরিপূর্ণ। তাঁর আদি নিবাস ছিল যশোর জেলায়। রেল না খোলায় তিনি নৌকা, গরুর গাড়ি এবং পদব্রজে এসে পীরগঞ্জে মোক্তারি ব্যবসা শুরু করেন। প্রথম জীবনে তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল অতি দুর্বল; মাসিক তেরো সিকেয় ভাড়া করা ঘরে নিজে রান্না করে খেতেন। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে তিনি পাকা দালান, বাগান, পুকুর এবং কোম্পানির কাগজ কিনে এলাকায় প্রখ্যাত মোক্তার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি ছিলেন মহারাজ নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরীর বাপের আমল থেকে বাঁধা মোক্তার। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনে নানা সমস্যা দেখা দেয়—নতুন নিয়মে শিক্ষিত মোক্তারদের আগমনে তাঁর ব্যবসা মন্দা হয়ে যায় এবং সংসারের ব্যয় বাড়তে থাকে। ষাট বছর বয়সে তিনি অবসর নেওয়ার কথা ভাবলেও কনিষ্ঠ পুত্র মানুষ না হওয়ায় পারেননি। জীবনের শেষ দিকে তাঁর নাতনীর বিয়ের দায় তাঁকে আবারও বিপাকে ফেলে। তবে তিনি কখনও দায়িত্ব এড়িয়ে যাননি। এক ইংরেজ জজ তাঁর কাজের প্রশংসা করলে তিনি জীবনের সব কষ্ট ভুলে যান। জয়রামের জীবন তাই এক সংগ্রামী ও আত্মসম্মানবোধে পরিপূর্ণ মানুষের প্রতিচ্ছবি, যিনি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মর্যাদা ও কর্তব্যকে সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন।
—
৩. ‘হাতী দিলে না। হাতী দিলে না!’—উক্তিটি কার? প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।
এই উক্তিটি জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের। ঘটনাটি ঘটে পীরগঞ্জের মেঝবাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে। জয়রাম মোক্তার ও তাঁর বন্ধুরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য রাজবাড়ি থেকে হাতি চেয়ে পাঠান। মহারাজ নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, যিনি এক সময় জয়রামের মক্কেল ছিলেন, তিনি হাতি দিতে অস্বীকার করে বলেন, “গরুর গাড়িতে চলে আসতে বলো।” এই খবরটি যখন জয়রামের কানে পৌঁছায়, তিনি গভীর অপমানবোধে আক্রান্ত হন। রাজবাড়ির এই প্রত্যাখ্যান তাঁকে যেন ভিতর থেকে নাড়িয়ে দেয়। তাঁর অভিমান, রাগ, লজ্জা এবং আত্মসম্মানবোধ মিশে এক ভয়ঙ্কর মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে। তিনি নিজের সম্মান ও মর্যাদার অপমান হিসেবে বিষয়টিকে গ্রহণ করেন। তাই ক্ষোভে, অপমানে, রোষে তিনি বারবার উচ্চারণ করেন—”হাতী দিলে না! হাতী দিলে না!” এই উক্তিটি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিক্রিয়া নয়, বরং এক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষের আহত গৌরবের প্রকাশও বটে। এই মুহূর্তে জয়রাম যেন নিজের সমস্ত জীবনব্যাপী আত্মসম্মানবোধকে আহত হতে দেখেন, এবং সেই তীব্র অভিমানই তাঁকে দুই হাজার টাকায় নিজের হাতি কেনার মতো উন্মত্ত সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করে।
—
৪. ‘- এ বিবাহে আমার যাওয়াই হবে না’—উক্তিটি কার? এখানে কার বিবাহের কথা বলা হয়েছে? বক্তা সেই বিবাহে যেতে চান না কেন?
এই উক্তিটি জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের মুখে উচ্চারিত। এখানে পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ির মেঝবাবুর মেয়ের বিবাহের কথা বলা হয়েছে। জয়রাম সেই বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে নগেন ডাক্তার ও কুঞ্জবিহারীবাবুও যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজবাড়ি থেকে হাতি না দিয়ে গরুর গাড়িতে যেতে বলা হলে জয়রাম তা নিজের প্রতি অপমান হিসেবে নেন। তিনি মনে করেন, মহারাজ তাঁর মর্যাদাকে অবমাননা করেছেন। তাই তিনি দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেন—”যদি হাতি চড়ে যেতে পারি, তবেই যাব, নয়তো এ বিবাহে আমার যাওয়াই হবে না।” তাঁর এই উক্তিতে ব্যক্তিগত অভিমান যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি তাঁর আত্মসম্মানবোধের দৃঢ় অবস্থানও ফুটে ওঠে। রাজবাড়ির কাছ থেকে হাতি না পাওয়া তাঁর কাছে সামাজিক অপমানের শামিল ছিল, কারণ রাজবাড়ির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক এবং কর্মনিষ্ঠা তিনি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ধারণ করতেন। সেই সম্পর্কের প্রতি অবজ্ঞা তাঁকে আহত করে। তাই এই উক্তিটি তাঁর আত্মমর্যাদাপূর্ণ চরিত্র, গভীর অভিমান এবং প্রতিবাদী মনোভাবের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত।
—
৫. মেঝবাবুর মেয়ের বিয়েতে যাওয়ার জন্য জয়রাম কী উপায় করলেন এবং কেন?
মহারাজ নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী যখন জয়রামকে হাতি দিতে অস্বীকার করলেন, তখন জয়রাম প্রচণ্ড রাগে ও অভিমানে জ্বলে ওঠেন। তিনি স্থির করেন, যে কোনও মূল্যে তিনি হাতি চড়ে যাবেন। তিনি সহর থেকে কয়েকজন জমিদারের কাছে হাতি কেনার চেষ্টা করেন। অবশেষে বীরপুরের জমিদার উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে তিনি দুই হাজার টাকায় একটি মাদী-হাতি ক্রয় করেন, যার নাম দেন “আদরিণী”। এই সিদ্ধান্ত ছিল একদিকে তাঁর আভিজাত্য ও মর্যাদার প্রতীক, অন্যদিকে তাঁর আত্মসম্মান রক্ষার এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। জয়রামের এই কাজ কেবল এক অহংকারের প্রকাশ নয়, বরং তাঁর জীবনের এক মানসিক জয়। রাজবাড়ির অবমাননার জবাবে তিনি নিজেই প্রমাণ করলেন যে, তিনি কারও অনুগ্রহে নির্ভরশীল নন। নিজের অর্থে হাতি কিনে তিনি সমাজের কাছে নিজের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে যেমন এক আত্মগরিমা প্রকাশ পায়, তেমনি দেখা যায় তাঁর একরোখা মনোভাব ও তীব্র আত্মবিশ্বাস। তাই এই ঘটনার মাধ্যমে জয়রাম চরিত্রের অভিমান, মর্যাদাবোধ ও প্রতিক্রিয়াশীলতা একসঙ্গে প্রতিফলিত হয়।
—
৬. আদরিণী কে? তার আগমনে গ্রামের কী অবস্থা হয়েছিল বর্ণনা করো।
আদরিণী হলো জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বীরপুর থেকে কেনা দুই হাজার টাকার মাদী-হাতী। সে কেবল এক পশু নয়, জয়রামের আত্মমর্যাদার প্রতীক ও স্নেহের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। যখন আদরিণী প্রথম জয়রামের বাড়িতে আসে, তখন গোটা গ্রাম যেন উৎসবে মেতে ওঠে। বাড়ির উঠোনে এবং আশেপাশে অসংখ্য বালক ভিড় করে দাঁড়ায় হাতিটিকে দেখার জন্য। কেউ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, কেউ আবার মজা করে বলে ওঠে—“হাতি তোর গোদা পায়ে নাতি।” এতে বাড়ির বালকেরা রেগে গিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেয়। বাড়ির ভিতরেও আদরিণীর আগমনে এক ধর্মীয় ও মঙ্গলাচরণের আবহ তৈরি হয়। জয়রামের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ ঘটিতে জল এনে তার পায়ে ঢেলে বরণ করেন, এরপর সিন্দুর ও তেল দিয়ে তার ললাট রাঙিয়ে দেন। শঙ্খধ্বনি ও আশীর্বাদধ্বনিতে পরিবেশ মুখর হয়ে ওঠে। রাজহস্তীর জন্য সংগৃহীত কলা, আলোচাল ও অন্যান্য খাদ্য তাকে খাওয়ানো হয়। আদরিণীর আগমন যেন এক আনন্দময় উৎসবের সূচনা করে, যেখানে গ্রামবাসী, পরিবার ও শিশুদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উল্লাস দেখা যায়। এই ঘটনা জয়রাম পরিবারের মর্যাদা, ঐশ্বর্য ও স্নেহবোধের প্রতীক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকে।
—
৭. জয়রামের বাড়িতে আদরিণীকে কীরূপে আপ্যায়ন করা হয়েছিল?
আদরিণীর আগমনে জয়রামের পরিবার তাকে যেভাবে আপ্যায়ন করে, তাতে বোঝা যায় এই প্রাণীটি কেবল একটি হাতি নয়, পরিবারের এক স্নেহভাজন সদস্য। যখন হাতিটি বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়ায়, তখন জয়রামের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ ঘটিতে জল এনে ভক্তিভরে তার পদচতুষ্টয়ে ঢেলে দেন। মাহুতের নির্দেশে হাতিটি জানু মুড়ে বসলে বধূ তার কপালে সিন্দুর ও তেল মেখে তাকে আশীর্বাদ করেন। আশেপাশে শঙ্খধ্বনি শুরু হয়, যেন এক দেবতার পূজা চলছে। এরপর রাজহস্তীর মতো করে তাকে আলোচাল, কলা ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্য অর্পণ করা হয়। আদরিণী আনন্দভরে সেগুলো ভক্ষণ করে। তার এই পূজনীয় মর্যাদা পরিবারে গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধার ইঙ্গিত বহন করে। জয়রামের কাছে আদরিণী ছিল কেবল এক পশু নয়, বরং তাঁর জীবনের গর্ব ও আত্মসম্মানের প্রতীক। তাই আদরিণীর এই বরণ-অভ্যর্থনা দৃশ্যটি গল্পে এক অনন্য আবেগপূর্ণ অধ্যায় হয়ে উঠেছে, যা মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে স্নেহের বন্ধনকেই প্রতিফলিত করে।
—
—
৮. আদরিণীকে নিয়ে গ্রামের বালকদের মধ্যে কী কাণ্ড ঘটেছিল?
আদরিণী যখন প্রথম জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসে, তখন গোটা গ্রামজুড়ে কৌতূহল ও উৎসাহের ঢেউ ওঠে। বিশেষ করে গ্রামের বালকেরা যেন উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। তারা দলে দলে এসে হাতিটিকে দেখতে বাড়ির উঠোনে, গেটের ধারে, রাস্তার পাশে ভিড় জমায়। আদরিণীর বিশাল শরীর, তার শুঁড়ের নাচন, আর গম্ভীর গর্জন দেখে তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়। কেউ আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে, কেউ আবার মজার ছলে বলতে থাকে— “হাতি তোর গোদা পায়ে নাতি।” এই কথায় জয়রামের বাড়ির বালকেরা রেগে গিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেয়, ফলে এক প্রকার হুলস্থুল কাণ্ড বেধে যায়। কেউ দৌড়ে পালায়, কেউ আবার পিছনে ফিরে হাত নেড়ে হাসে। এই দৃশ্যটি গ্রামীণ জীবনের এক স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও শিশুসুলভ কৌতূহলের প্রতিচ্ছবি। আদরিণীর আগমন যেন তাদের কাছে এক নতুন খেলনা বা আশ্চর্যের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। গল্পের এই অংশে লেখক শিশুমনের সরলতা ও প্রাণবন্ততা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেইসঙ্গে বোঝানো হয়েছে, আদরিণীর আগমন কেবল জয়রামের মর্যাদাবোধের পুনরুদ্ধার নয়, গোটা গ্রামের আনন্দ-উৎসবেরও এক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল।
—
৯. জয়রাম মুখোপাধ্যায় কেমন মানুষ ছিলেন — তোমার মতামত লেখো।
জয়রাম মুখোপাধ্যায় ছিলেন এক জটিল অথচ বাস্তব চরিত্র। তাঁর মধ্যে যেমন ছিল কঠোর আত্মসম্মান, তেমনি ছিল কোমল মানবিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা। তিনি জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজের অবস্থান গড়ে তুলেছিলেন। প্রাথমিক জীবনে তিনি ছিলেন দরিদ্র; নিজে রান্না করে খেতেন, কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর অধ্যবসায় ও সততা তাঁকে সমাজে সম্মানিত করে তোলে। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ মোক্তার, গরীব ক্লায়েন্টদের জন্য বিনা ফিসে মামলা চালাতেন। তবে তাঁর প্রধান দোষ ছিল প্রবল অভিমান ও আত্মগরিমা। রাজবাড়ি থেকে হাতি না পাওয়ায় তিনি যেভাবে দুই হাজার টাকায় হাতি কিনে ফেললেন, তাতে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধের পাশাপাশি একরোখা মনোভাবও প্রকাশ পায়। তিনি অহংকারী ছিলেন না, কিন্তু নিজের মর্যাদা রক্ষায় কখনো আপস করতেন না। পরিবারের প্রতি তাঁর স্নেহ ও দায়িত্ববোধও প্রবল ছিল। শেষ বয়সে তিনি শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতির অভাবে মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও নিজের কর্তব্যে অবিচল ছিলেন। সবদিক মিলিয়ে জয়রাম মুখোপাধ্যায় ছিলেন এক সংগ্রামী, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন এবং গভীর মানবিক গুণে পরিপূর্ণ চরিত্র, যাঁর জীবনে সাফল্য, মর্যাদা ও অভিমান একসঙ্গে মিশে গেছে।
—
১০. জয়রামের জীবনে ‘আদরিণী’-র প্রতীকী তাৎপর্য কী?
‘আদরিণী’ কেবল একটি হাতি নয়; সে জয়রামের আত্মমর্যাদা, গর্ব, ও ব্যক্তিত্বের প্রতীক। রাজবাড়ি থেকে হাতি না দেওয়ার অপমানে যখন জয়রামের আত্মসম্মান আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখন ‘আদরিণী’-র আগমন সেই ক্ষতস্থানে এক প্রতিক্রিয়া হিসেবে আসে। হাতিটি কেনা ছিল কেবল বাহ্যিক বিলাস নয়—এটি ছিল নিজের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের ঘোষণা। আদরিণীর নামের মধ্যেই আছে স্নেহ ও আদরের ছোঁয়া; জয়রাম তাকে কেবল বাহন হিসেবে নয়, পরিবারের সদস্যের মতো ভালোবেসেছিলেন। ফলে ‘আদরিণী’ তাঁর একাকিত্ব ও আত্মগরিমার প্রতীকও বটে। গল্পের শেষভাগে আদরিণীর মাধ্যমে জয়রামের জীবনে আবারও এক উজ্জ্বলতা ফিরে আসে—মানুষের শ্রদ্ধা, পরিবারের আনন্দ, এবং নিজের অভিমানের প্রশমিতি। তাই প্রতীকী দিক থেকে আদরিণী হলো এক জীবন্ত চিত্র, যা জয়রামের আহত আত্মসম্মানের পুনর্জন্মকে নির্দেশ করে। লেখক আদরিণীর মাধ্যমে দেখিয়েছেন, বাহ্যিক মর্যাদা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, মানুষের অন্তরের মর্যাদাবোধই প্রকৃত সম্পদ।
—
১১. জয়রামের জীবনের শেষদিকে তিনি কেমন ছিলেন?
জীবনের শেষ প্রান্তে জয়রাম মুখোপাধ্যায় ছিলেন ক্লান্ত, একাকী এবং অতীত-স্মৃতিতে বিভোর এক মানুষ। যৌবনে তিনি ছিলেন উদ্যমী, আত্মমর্যাদাবান ও কর্মনিষ্ঠ মোক্তার; কিন্তু বয়সের ভার, পারিবারিক দায়িত্ব এবং পেশাগত প্রতিযোগিতা তাঁকে ধীরে ধীরে ক্লান্ত করে তোলে। নতুন শিক্ষিত মোক্তারদের আগমনে তাঁর কাজ কমে যায়, ফলে আর্থিক সঙ্কটও দেখা দেয়। সংসারের দায়ভার ও নাতনীর বিয়ের চিন্তা তাঁকে মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত করে। তবুও তিনি দায়িত্ব থেকে পলায়ন করেননি। জীবনের শেষ সময়ে তিনি এক ইংরেজ জজের কাছ থেকে সামান্য প্রশংসা পেয়ে গভীরভাবে আলোড়িত হন। এই ঘটনা তাঁর জীবনের এক প্রকার আত্মতৃপ্তি এনে দেয়, কারণ তিনি বুঝতে পারেন, জীবনের পরিশ্রম বৃথা যায়নি। শেষ বয়সে তাঁর মধ্যে যে একাকিত্ব ও ক্লান্তি, তা বাস্তব জীবনের প্রবীণ মানুষের অবস্থা প্রতিফলিত করে। জয়রাম ছিলেন সমাজে সম্মানিত, কিন্তু অন্তরে এক অপূর্ণতার বোধ ছিল। তাই তাঁর জীবনের শেষ পর্ব একদিকে বিষণ্ণ, অন্যদিকে মর্যাদায় দীপ্ত—এক অনন্য মানবিক ট্র্যাজেডি ও গৌরবের মিশেল।
—
১২. ‘আদরিণী’ গল্পের মূল ভাবটি কী?
‘আদরিণী’ গল্পের মূল ভাব হলো মানুষের আত্মসম্মান, মর্যাদাবোধ এবং সমাজে নিজের অবস্থান রক্ষার মানসিক সংগ্রাম। জয়রাম মুখোপাধ্যায়, যিনি সারা জীবন সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন, রাজবাড়ির এক অবহেলাতেই নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। এই অভিমান থেকেই তিনি নিজের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের প্রতীক হিসেবে হাতি কিনে আনেন — ‘আদরিণী’। এই হাতিটি তাঁর আত্মমর্যাদার প্রতীক হয়ে ওঠে। গল্পে লেখক দেখিয়েছেন, মানুষের জীবনে অর্থ বা বস্তুগত সাফল্যের চেয়ে সম্মানবোধ অনেক বড়। জয়রামের চোখে মর্যাদা হারানো মানেই জীবন হারানো। পাশাপাশি গল্পে আছে মানবিকতা, পারিবারিক বন্ধন, এবং সমাজে পরিবর্তনের প্রভাবের ইঙ্গিত। নতুন যুগের আগমন যেমন জয়রামের জীবনে কষ্ট নিয়ে আসে, তেমনি তাঁর আত্মগরিমা তাঁকে অমর করে তোলে। তাই গল্পের মূল বার্তা — “আত্মসম্মানই মানুষের প্রকৃত অলংকার।”
—
১৩. জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের জীবনে অভিমান কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল?
অভিমান জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রের এক প্রধান চালিকাশক্তি। তাঁর জীবনের অনেক সিদ্ধান্তই এসেছে অভিমান থেকে। মহারাজের হাতি না দেওয়ার ঘটনায় তাঁর গভীর আত্মসম্মান আহত হয়। সেই আঘাত থেকে জন্ম নেয় প্রবল অভিমান, যা তাঁকে দুই হাজার টাকায় হাতি কিনতে বাধ্য করে। এই অভিমানই তাঁর গর্ব ও মর্যাদাবোধকে রক্ষা করলেও কখনো কখনো তাঁকে বাস্তববোধ থেকে বিচ্যুত করেছে। জীবনের শেষে তিনি অনুভব করেন, হয়তো তাঁর কঠোর অভিমানই তাঁকে পরিবার ও সমাজ থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তবুও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনুতপ্ত নন, কারণ সেটিই তাঁর আত্মমর্যাদার প্রতীক। জয়রামের অভিমান একদিকে তাঁর চরিত্রকে জীবন্ত করেছে, অন্যদিকে তাঁর জীবনের সুরকে করেছে গম্ভীর ও গৌরবময়। বলা যায়, অভিমানই ছিল তাঁর আত্মার প্রকাশ — যা তাঁকে সাধারণ থেকে অসাধারণ করে তুলেছিল।
—
১৪. জয়রামের জীবনে নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরীর ভূমিকা কী?
নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী পীরগঞ্জের মহারাজ এবং জয়রামের প্রাক্তন মক্কেল। তিনি গল্পে প্রত্যক্ষভাবে বেশি উপস্থিত না থাকলেও, তাঁর একটি সিদ্ধান্ত পুরো গল্পের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। মহারাজ যখন জয়রামকে হাতি না দিয়ে “গরুর গাড়িতে চলে আসতে বলো” — এই অবহেলামূলক বাক্য বলেন, তখনই জয়রামের আত্মসম্মান চরমভাবে আহত হয়। এই ঘটনা তাঁর জীবনে এক মোড় ঘুরিয়ে দেয়, কারণ এখান থেকেই ‘আদরিণী’-র আগমন এবং তাঁর আত্মমর্যাদার পুনর্গঠন শুরু হয়। তাই বলা যায়, নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী জয়রামের জীবনে এক প্ররোচনাকারী চরিত্র — তাঁর অবহেলাই জয়রামের আত্মগরিমার পুনর্জন্ম ঘটায়। প্রতীকী অর্থে, রাজবাড়ি হলো ক্ষমতার প্রতীক এবং জয়রাম হলো আত্মসম্মানের প্রতীক। এই দুইয়ের সংঘাতেই গল্পের মূল নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়।
—
১৫. জয়রামের সঙ্গে নগেন ডাক্তার ও কুঞ্জবিহারীর সম্পর্ক কেমন ছিল?
নগেন ডাক্তার ও কুঞ্জবিহারী ছিলেন জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল। তাঁরা সবাই সমাজে শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, এবং প্রায়ই মেলামেশা করতেন। বিয়েতে হাতি না পাওয়ার ঘটনায় নগেন ডাক্তার ও কুঞ্জবিহারী জয়রামকে শান্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জয়রামের অভিমান এত প্রবল ছিল যে তিনি তা শোনেননি। তবুও বন্ধুরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারাননি; বরং তাঁর একরোখা স্বভাব দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। গল্পের এই সম্পর্কের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, বন্ধুত্ব কখনো কখনো ভিন্ন মত হলেও শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। জয়রামের বন্ধুদের চোখে তিনি ছিলেন “গৌরবের মানুষ”— এক সম্মাননীয়, আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তি।
—
১৬. জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের জীবন থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায়?
জয়রামের জীবন আমাদের শেখায় যে আত্মসম্মান ও সততা মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ। জীবনে যতই অর্থ বা খ্যাতি আসুক, যদি নিজের মর্যাদা হারিয়ে ফেলি, তবে সবই অর্থহীন। তিনি দেখিয়েছেন যে নিজের পরিশ্রম ও সততার মাধ্যমে সমাজে সম্মান অর্জন সম্ভব। তবে অতিরিক্ত অভিমান কখনো জীবনে বিচ্ছিন্নতা আনতে পারে, সেটিও তাঁর জীবনের মাধ্যমে শিক্ষা মেলে। জয়রাম ছিলেন এক কর্তব্যপরায়ণ, আত্মমর্যাদাবান ও পরিশ্রমী মানুষ, যিনি নিজের অবস্থান তৈরি করেছিলেন নিজ হাতে। তাঁর জীবন তাই এক অনুপ্রেরণার উদাহরণ—মানুষের শ্রদ্ধা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না, তা অর্জন করতে হয় কর্মে ও মর্যাদায়।
—
১৭. ‘আদরিণী’ গল্পে লেখকের বর্ণনাশৈলী সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।
লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর বর্ণনাশৈলীতে অসাধারণ প্রাণবন্ততা ও হাস্যরস মিশিয়েছেন। গল্পটি একেবারে বাস্তবধর্মী; গ্রামীণ পরিবেশ, চরিত্রের সংলাপ, এবং বাঙালি সমাজের সংস্কার সবকিছুই স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠেছে। লেখকের ভাষা সংযত, অথচ প্রাঞ্জল ও ব্যঙ্গরসপূর্ণ। জয়রামের অভিমান, গ্রামের বালকদের কাণ্ড, আদরিণীর আগমন—সব কিছু এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে যে পাঠক যেন দৃশ্যগুলো চোখের সামনে দেখতে পান। চরিত্রগুলোর সংলাপে রয়েছে জীবন্ত রসবোধ ও সূক্ষ্ম মানবিকতা। লেখক জয়রামের চরিত্রের মাধ্যমে একদিকে আত্মমর্যাদার গৌরব, অন্যদিকে অভিমানের ট্র্যাজেডি দেখিয়েছেন। সব মিলিয়ে, ‘আদরিণী’ গল্পের ভাষা ও বর্ণনাশৈলী পাঠককে একদিকে হাসায়, অন্যদিকে চিন্তায় নিমগ্ন করে—যা সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্যরীতিের আসল বৈশিষ্ট্য।
তাৎপর্য
১. ‘তাই ত! সব মাটি?’ – নগেন ডাক্তার
এই উক্তিটি নগেন ডাক্তার করেছিলেন, যখন জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের চিঠি অনুযায়ী রাজবাড়ি থেকে হাতি পাওয়া যায়নি। জয়রামের নিমন্ত্রণ পালনের আশা তখন ভঙ্গ হয়, এবং নগেন ডাক্তার হতাশা ও অবিশ্বাস প্রকাশ করতে এই কথাটি বলেন। “সব মাটি” শব্দগুচ্ছটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এটি শুধু হতাশার প্রতীক নয়, বরং সামাজিক ও বাস্তবিক সীমাবদ্ধতার দিকে ইঙ্গিত করে। জয়রামের তীব্র অভিমান ও রাগের সঙ্গে এই বাস্তববাদী প্রতিক্রিয়া juxtaposition হিসেবে দাঁড়ায়। এটি পাঠককে বোঝায় যে, জীবনের প্রতিটি ইচ্ছা বা পরিকল্পনা সবসময় সফল হয় না, এবং মানুষকে কখনও বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। নগেন ডাক্তার এর মাধ্যমে গল্পে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরিত্রগুলোর আবেগের গভীরতা ফুটে ওঠে, যা পাঠককে চরিত্রের মানসিক অবস্থা অনুধাবনে সাহায্য করে।
—
২. ‘পরের জিনিষ, জোর ত নেই।’ – ভদ্রলোকগণ
এই উক্তিটি সমবেত ভদ্রলোকদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় জয়রামকে শান্ত করার জন্য। যখন মহারাজ নরেশচন্দ্র হাতি দিতে অস্বীকার করেন, জয়রাম ক্ষিপ্ত ও হতাশ হয়ে ওঠেন। ভদ্রলোকগণ বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, হাতি অন্যের জিনিস, তাই জোর করে আনা সম্ভব নয়। এটি বাস্তবতার সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক নিয়ম মেনে চলার গুরুত্ব বোঝায়। জয়রামের অভিমান, রাগ এবং হতাশার সঙ্গে তাদের শান্তিমূলক পরামর্শ juxtaposition হিসেবে গল্পে আবেগ ও যুক্তির ভারসাম্য দেখায়। পাঠক বুঝতে পারে যে, কখনও কখনও ইচ্ছার সাথে বাস্তবতার মিল ঘটানো কঠিন হলেও, মানুষকে তা মেনে চলতে হয়। এটি গল্পে শিক্ষণীয় দিকও প্রদান করে, যা চরিত্রের অভ্যন্তরীণ মনস্তত্ত্ব এবং সামাজিক আচরণের প্রতি সমঝোতার গুরুত্ব বোঝায়।
—
৩. ‘…ওদের একে একে বিক্রী করে ফেল।’ – জয়রাম মুখোপাধ্যায়
এই উক্তিটি জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা উচ্চারিত, যখন তাঁর বন্ধু-বান্ধব আদরিণীকে বিক্রি করার পরামর্শ দেন। জয়রাম রাগ ও দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, যদি কেউ বিক্রি হয়, তা সন্তানের মতো প্রিয় প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। এটি তার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্নেহ এবং পরিবারের প্রতি গভীর আবেগ প্রকাশ করে। আদরিণী তাঁর কাছে শুধুই পোষ্য নয়, বরং পরিবারের সদস্য বা কন্যার মতো। এই প্রতিক্রিয়া পাঠককে বোঝায় যে, মানব জীবনে সংযুক্তি এবং স্নেহ কোনো মূল্য বা সম্পদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। বিজনেস বা অর্থনৈতিক প্রস্তাবের বিপরীতে মানুষের আবেগ ও দয়া কখনও কখনও শক্তিশালীভাবে প্রভাব ফেলে। জয়রামের এই উক্তি গল্পে আদরিণীর প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্বকে শক্তভাবে তুলে ধরে।
—
৪. ‘যেনো হারাধন ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে’
এই উক্তিটি ব্যবহৃত হয়েছে যখন আদরিণী প্রথমবার মেলা থেকে বিক্রি না হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। আদরিণীর ফিরে আসায় পরিবার আনন্দে মুখরিত হয়। এটি বোঝায় যে, প্রিয় প্রাণীকে মানুষ কেবল সম্পদ হিসেবে নয়, বরং আত্মীয়ের মতো অনুভব করে। জয়রামের আনন্দ, স্নেহ এবং আদরিণীর প্রিয়তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। পাঠক বুঝতে পারে যে, জীবনের ছোট্ট সুখও পরিবারের আবেগ ও সম্পর্কের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আদরিণীকে প্রিয় হিসেবে দেখা, তার আগমন ও আনন্দময় অভিজ্ঞতা গল্পে মানবিক অনুভূতি এবং স্নেহের গুরুত্বকে তুলে ধরে। এটি চরিত্রগুলোর আবেগিক সম্পর্ক এবং মানব-পশু বন্ধনের গভীরতা প্রকাশের একটি শক্তিশালী উপায়।
—
৫. ‘ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল।’ – জয়রাম মুখোপাধ্যায়
এই উক্তি প্রকাশ করে জয়রামের চরম মানসিক আঘাত এবং দুঃখ। আদরিণীর মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি ধ্বংসপ্রায় শোকের মধ্যে পড়েন। এখানে ‘ব্রাহ্মণ’ অর্থ জয়রাম, যিনি অত্যন্ত স্নেহশীল ও আবেগপ্রবণ। উক্তি পাঠককে বোঝায় যে, প্রাণীর প্রতি গভীর স্নেহ ও আবেগ মানুষের আবেগকে শক্তিশালীভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এটি তার অন্তর্যামী অনুভূতি, দায়বোধ এবং পোষ্য-প্রেমের প্রমাণ। আদরিণীর মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁর মানসিক ও আবেগিক অবস্থার চরম প্রকাশ ঘটেছে, যা পাঠককে চরিত্রের গভীর মানবিকতা এবং আবেগের জটিলতা অনুধাবনে সাহায্য করে। এই মুহূর্তটি গল্পের আবেগিক চূড়ান্ত বিন্দু এবং পাঠককে চরিত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে।
ব্যাকরণ অধ্যয়ন। (Grammar Study)
সমাস
সমাস হলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দুই বা দুইয়ের অধিক পদের এক পদে পরিণত হবার নাম।
সমাস সাধারণত ছয় প্রকার— দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব ও বহুব্রীহি।
দ্বন্দ্ব সমাস: যে সমাসে সমস্যমান প্রত্যেকটি পদের অর্থের সমান প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। (যেমন: নগেন ডাক্তার ও জুনিয়ার উকিল)
তৎপুরুষ সমাস: যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান হয় এবং পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়। (যেমন: সিংহের ন্যায় বিক্রম (সিংহবিক্রম – ষষ্ঠী তৎপুরুষ)
কর্মধারয় সমাস: যে সমাসে বিশেষ্য ও বিশেষণে বা কেবল বিশেষ্য বা কেবল বিশেষণে সমাস হয় এবং পরপদের অর্থ প্রধান হয়। (যেমন: মেঝবাবু (মেজ যে বাবু – সাধারণ কর্মধারয়), সুশীল (সু বা ভালো যে শীল – সাধারণ কর্মধারয়))
দ্বিগু সমাস: যে সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্যের সমাস হয় এবং সমষ্টি বা সমাহার বোঝায়। (যেমন: সাত ক্রোশ (সাত ক্রোশের সমাহার))
অব্যয়ীভাব সমাস: যে সমাসে পূর্বপদটি অব্যয় হয় এবং সেই অব্যয়ের অর্থ প্রধান হয়। (যেমন: প্রতি বৎসর (বৎসর বৎসর))
বহুব্রীহি সমাস: যে সমাসে সমস্যমান কোনো পদের অর্থই প্রধান না হয়ে অন্য কোনো পদের অর্থ প্রধান হয়। (যেমন: বিপত্নীক (বিগতা পত্নী যার – নঞর্থক বহুব্রীহি))